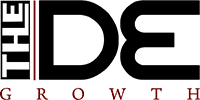তিনটি নদীর মিলন স্থলকে বলে ত্রিবেণী। এখানে দুটি নদীর মিলন হয়ে মোহনা হয়েছে। একটি মূল নদী চিত্রা আর এই মূল নদীর সঙ্গে অন্য একটি নদী ফটকী এসে যোগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছে মোহনা। মোহনা র তিনটি পাড়ে তিনটি গ্রাম যথাক্রমে সোনাকুড়;দেশমুখপাড়া ও কুয়াৎপুর এই কুয়াপুর গ্রামেই আমার জন্ম। শিশুবেলায় দেখেছি এই গ্রামের প্রথম বাড়ীটার শেষের দিকে ছিল একটি আমগাছ যা মোহনার পাড়েই। প্রথম বাড়ীটার পরেই আমাদের বাড়ী। আমরা সাধারণত নদীর দুটো ঘাটই ব্যবহার করতাম। একটা ঘাট ছিল কর্দমাক্ত অন্যটি ছিল একদমই বেলে। আর এইটাই ছিল ব্যবহারিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যে আম গাছটি ছিল সেই গাছের ছায়ায় শিশুদের জন্য একটি বিদ্যালয় ছিল। একজন বিনা পারিশ্রমিকের শিক্ষক ছিলেন, যাঁর নাম রইজ মাস্টার। তাঁর বাড়ী ছিল মোহনা থেকে তিন কিলোমিটার দূরে মধুখালী গ্রামে। বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ছিল মেরে কেটে ৮-১০ জন। তারা সবাই মৎসজীবী পরিবারের দড়ি বাঁধা হাফপ্যান্ট পরা ছাত্র। মাস্টার সাহেবকে আমরা দাদু বলে ডাকতাম। দাদু মাস্টার চেহারায় ছিলেন এক লৌহবৎ শিক্ষানুরাগী। তুষার ধবল কেশ ও দাড়ি বিশিষ্ট মমতাময় সুপুরুষ। বয়স তখন ছিল ষাটের কোঠায়। তিনি ছাত্রদের হাতে খড়ি দিতেন এবং পড়া না করলে শাস্তি দিতেন। যারা তাঁর ছাত্র ছিলেন তারা কেউই প্রায় প্রথম ভাগ বা দ্বিতীয় ভাগের গন্ডী পেরোতে পারেনি। এই দাদু মাস্টারের মূল্যায়ণ করার মতো বিদ্যা একজন ছাত্র ছাড়া আর কেউই অর্জন করতে পারে নি। আর সেই ছাত্রটি ছিলেন আমার নিজের দাদা তারাপদ। তিনি ১৯৬১ সালে বি এ পাশ করেন এবং বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিব বাহিনী তাকে গুলি করে মারার কারণে সেই মূল্যায়ণ তিনি করে যেতে পারেন নি। এর ফলে দাদুর মূল্যায়ণ যেমন হয় নি, আমাদের পরিবারের পক্ষেও তা ছিল এক অস্তমান সূর্যের প্রতীক। আর একটা কথা এই পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় আমার যে সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে সেখানে ভুলক্রমে লেখা হয়েছে আমি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছিলাম। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। আমি পাশ বিভাগে পাশ করি।
আমার এই লেখায় দাদু মাস্টারের প্রসঙ্গ আনলাম এই কারণেই যে,দাদুর দেওয়া নামটাই ছিল। এই মোহনার নাম “যদুখোলা”। শুনেছিলাম দাদুর এক অকৃতদার বন্ধুর নাম ছিল ‘যদু” আর তার নামেই এই নামকরণ, এই নামেই মোহনার পরিচিতি।
মোহনার চিত্রা আর ফটকী নদীর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। চিত্রা নদী ও ফটকী নদী উজানে একটি পশ্চিমাভিমুখী ও অন্যটি উত্তরাভিমুখী। চিত্রা নদী আমাদের গ্রামের গা ঘেষে বাণিজ্য শহর বুনাগাতি,শালিখা,নারিকেল বাড়ীখা ও মাজুরার দিকে চলে গেছে। এর উৎস মুখ মরা। শুনেছি পদ্মাই ছিল এর উৎস মুখ,শালিখা পর্যন্ত এর নাব্যতা ছিল। দু তীরেই ছিল ঘনবসতি গ্রাম। মাঝে মধ্যে উভয় তীরেই ছিল কিছু খাল ও খালের শেষে বা মাথায় ছিল বিল আর সেই বিলের জল সহজেই এই সমস্ত খাল দিয়ে নদীতে এসে পড়ত। নদীটির দূ-কূলের কিছুটা ছিল পাটা শেওলায় বেষ্টিত। মাঝখানে পরিষ্কার যার মাঝখান দিয়েই নৌকা চলাচল করত। এমনকি বুনাগাতী পর্যন্ত সেই সময় শিল্পশহর ‘দৌলতপুর’ থেকে যাত্রীবাহী লঞ্চ নিয়মিত আসতো। এ ছাড়া কৃষিপণ্য বহন করে বড় বড় নৌকো বুনাগাতী থেকে খুলনা ও দৌলতপুরে যেতো। ওখানে স্থল সড়কের অভাব ছিল। চিত্রা নদীতে ও নদীমুখী শাখা খাল। বিলে যথেষ্ট পরিমাণ দেশী মাছ থাকত।
মহোনার অন্য একটি নদী ‘ফটকী’ উজানে কুচিয়া মোড়া, আসবা-বরই চারা গ্রামের মাঝ দিয়ে আড়পাড়ী শহর ঘেঁষে বাণিজ্য বাজার ভাবনাটি হয়ে কালিগঞ্জের দিকে গিয়েছে। এটারও নাকি পদ্মার সঙ্গে একসময় যোগাযোগ ছিল। তখন এর মাথাটা ছিল জলহীন, ছিল শুধু নদীর ধারাটা মাত্র। আড় পাড়ার ভাটিতে এসে চিত্রার সঙ্গে একটা মরা নদী এসে মিশেছে। বছরের ৮ মাস এই নদীতে কোন জল থাকত না । নদীটার উৎসস্থল মাগুরা শহরের পুরানো বাজারের নবগঙ্গা নদী থেকে। নদীটির নাম ‘হাওড়” । বর্ষাকালে কানায় কানায় ভর্তি নবগঙ্গার উদ্বৃত্ব জল ধারণ ক্ষমতা যখন থাকত না,সেই উদ্বৃত্ব জলধারণ ক্ষমতা যখন থাকত না – সেই উদ্বৃত্ব জল এই হাওড় দিয়ে এসে খরস্রোতা ফটকী নদীতে পড়তো। নবগঙ্গা পদ্মার শাখা নদী। স্বভাবিকই বর্ষাকালে ঘোলাজল এই নদী দিয়ে প্রচন্ড গতিতে তার অভীষ্টের লক্ষ্যে পৌঁছত। সেই জলের সঙ্গে দেশী মাছের মীন বা ধাত্রী পোনা বহন করে হাওড় নদী দিয়ে এসে ফটকীতে পড়তো। আর ফটকীর নীচের দিকে ভাসমান কয়েকটি গ্রাম ছাড়া প্রায় সবই বিল ও মাঠ। এর মধ্যে নামকরা বড়বিল হলো ‘বুরোলী বিল। এই বিলের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এখানে আউস ও আমন দুরকম ধান একই সঙ্গে বোনা হতো। বর্ষাকালে ঘোলাজলের পুরোটাই দু- তীরের বিলকে পূর্ণ করে দিত। প্রায় আড়াই থেকে তিন মাস এই বিলে জল থাকত। একটা বিরাটাকারের উর্বর পলিও এই বিলের জমিতে পড়ত ফলে রাসায়নিক সারের কোন প্রশ্নই থাকত না। তখন রাসায়নিক সার ছিলও না। আড়াই থেকে তিন মাস এই বিলে জল থাকায় আমন ধান যেমন জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠত ঠিক তেমনি বেড়ে উঠত ক্ষণস্থায়ী বসবাস করা দেশী মাছ। কার্তিক মাসে যখন এই বিলের জল নদীতে নেমে আসত এবং নদীর কিনারা জেগে যেত, আমন ধানের মধ্যে পুষ্ট হওয়া মাছগুলি বাধ্য হয়ে নদীতে নামতে শুরু করতো আর মৎসজীবীসহ সাধারণ মানুষ মাছ ধরার উৎসবে মেতে উঠত। কতরকমের মাছ যেমন – পুঁটি, সরপুঁটি, গলদা চিংড়ি, পাপদা, ভেদা, বাউষ, আড়,রুই, কাতলা, মৃগেল ও চেতল ইত্যাদি মৎসশিকারীদের জালে ধরা পড়ত। কুচিয়া মোড়ায় ছিল মৎসজীবীদের বাস । তাঁরা তাদের ঘাটের নীচেই বাঁধ দিয়ে সুরি জাল পাততো। সেই জালে এত মাছ পড়ত যে অনেক সময় মাছ জাল থেকে ছেড়ে দিতে হতো। এর প্রায় পাঁচ কিলোমিটার নীচে / ভাটি মোহনার ধারে আরো বেশ কিছু মৎসজীবী বাস করতো। তারা মিলিতভাবে এই বাধ দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিল।
এই মানচিত্রেই বাস করত দেশী মাছের চারা। প্রায় তিন মাস ধরে তারা বেড়ে উঠত। কার্তিক মাসে যখন বিলের জল নেমে গেলে মাছ ধরা শুরু হতো। কুচিয়া মোড়া গ্রামে বেশ কিছু মৎসজীবী বসবাস করতো যারা তাদের গ্রাম সংলগ্ন নদীতে একটা সুতি জালের বাধ দিয়ে মাছ ধরত, তারাও বেশী মাছ ধরা পড়লে জাল থেকে নদীতে ছেড়ে দিতো। নদীর প্রায় ১০ কিমি নীচের দিকে একটা বড়মাপের মৎসজীবী গ্রাম ছিল। সুতি জালের বাধের জন্য মাছ সেখানে সহজে যথেষ্ট পরিমাণে আসত না। ফলে কুচিয়া মোড়ার মৎসজীবীদের সাথে মগরা কোর্টে অনেক কেসও হয়েছে। কিন্তু বাঁধ ঠেকাতে পারে নি। কারণ কুচিয়া মোড়ার পক্ষে ছিল প্রতিপত্তিশালী কর্ণধর মাঝি আর মোহনার মৎসজীবীদের পক্ষে কেস দেখভাল করত নটবর বিশ্বাস, যার প্রতিপত্তি ছিল কম। তবুও মহনায় যে মাছ পড়ত তাতে মৎসজীবী। সাধারণ মানুষের মধ্যে মাছ ধরার উৎসব লেগে যেত। কিছু মাছ মোহনার দুই নদী চিত্রা ও ফটকীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করত সারা বছর যা ধরে মোহনার ও আশেপাশের গ্রামের মৎসজীবীরা জীবিকা নির্বাহ করত। মাছ ধরার উপকরণ ছিল নৌকাভেসালী,বাড়েজাল, খেবলা জাল ইত্যাদি।
মূল নদী চিত্রা ভাটির দিকে দৌলতপুর ও খুলনা শহরের পাশে রূপসা নদীতে মিশে জলবন্দর মোঙ্গলা পোর্ট হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এই বঙ্গোপসাগর থেকে ফাল্গুন মাসের দিকে জোয়ার এর জলে কিছু বড় ইলিশের সঙ্গে প্রচুর ঝাটকে মাছ আসতো। আসতো ইলিশ মাছের পোনা যাকে খোটে বলা হতো। তাদের চারণ সাধারণত একটু গভীর জলে থাকত। ভাটার টানে জল যখন নদীতে কমে যেত তখন এই ঝটকে মাছগুলি জালে ধরা পড়ত। সেই মাছের স্বাদ না খেলে বোঝা যাবে না।।। এরা ফাল্গুন মাস থেকে আষাঢ় মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত চারণ করত। আষাঢ় মাসে ঘোলা জল এলেই এরা আবার বঙ্গোপসাগরের দিকে চলে যেত। [চলবে]