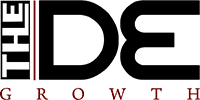১
চা পাতা সংগ্রহের প্রচলিত সময় সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। কিন্তু যদি সেই পাতা সংগ্রহ করা হয় পূর্ণিমা রাতের চাঁদের আলোয়, তাও বাছাই করা দক্ষ মহিলা শ্রমিকদের দিয়ে? চা ব্যবসার সাম্রাজ্যে এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত কৃষিজ ফসলটির নাম ‘মুনলাইট টি’। সমঝদার চা রসিকদের কাছে এ চায়ের কদর আকাশছোঁয়া। চলতি বছরে দার্জিলিংয়ের বাদামতাম চা বাগানের মুনলাইট চা বিক্রি হয়েছে কেজি প্রতি ২১ হাজার টাকায়। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের বিশেষ সময় অভিজ্ঞ শ্রমিক দিয়ে সংগৃহীত একটি প্রথম শ্রেণির চায়ের নাম ‘ফার্স্ট ফ্লাশ টি’। দার্জিলিংয়ের মকাইবাড়ি টি এস্টেট থেকে বিভিন্ন সময়ে এই চা বিক্রি হয় ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা প্রতি কেজিতে। চলতি বছরে বাদামতাম চা বাগান থেকে ফার্স্ট ফ্লাশ চা বিক্রি হয়েছে কেজিপ্রতি ২৩ হাজার টাকায়। কিংবদন্তি সুগন্ধি দার্জিলিং চায়ের দেশের বাজারে এটাই রেকর্ড দাম। দেশের বাজারে সবচেয়ে দামি চায়ের যোগান দেয় উত্তর পূর্ব ভারত, প্রধানত আসাম। ২০১৯ সালে আসামের মনোহারী চা বাগানের ‘সোনালী স্পেশালিটি’ চায়ের দাম উঠে ছিল কেজিপ্রতি ৫০ হাজার টাকা! যে কোনও গুণমান এবং পরিপ্রেক্ষিতে, আজকের তারিখ পর্যন্ত, দেশের বাজারে এটাই চায়ের সর্বোচ্চ দাম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সোনালী স্পেশালিটি চা তৈরি হয় পাতা থেকে নয়, কুঁড়ি থেকে। মেশিনের বদলে হাতে তৈরি এই চা-কে বলা হয় ‘এক্সকুইজিট স্পেশালিটি অর্থোডক্স টি’। ঠিক তার আগের বছর, ২০১৮ সালে এই চায়ের দাম উঠে ছিল কেজিপ্রতি ৩৯ হাজার টাকা। সে বছর মনোহারি বাগানের চা-কে পিছনে ফেলে সর্বোচ্চ দাম পেয়েছিল অরুণাচল প্রদেশের ডনিপোলো বাগান, কেজিপ্রতি ৪০ হাজার টাকা!

তো এতসব দামী দামী ব্যাপারের মধ্যে কমদামি কিছু আছে নাকি? আছে বৈকি! চা বাগানের ব্যবসার প্রথম পর্বে বাগান তৈরির জন্য অত্যন্ত কম দামে জমি পেয়েছিল ব্রিটিশ চা ব্যবসায়ীরা। এমনকি স্বাধীনতার পরেও উঠতি ভারতীয় চা ব্যবসায়ীরা কম দামের জমি এবং বিপুল কর ছাড়ের সুবিধা পেয়েছিল। এখনও চা বাগান এবং কারখানার কর্মীরা দৈনিক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কমদামি চাল-ডাল পেয়ে থাকেন। এখনও কলকাতা শহরের ফুটপাতে কোন বেকার বা আধা বেকার কম দামে এক ভাঁড় চা আর দুটো বিস্কুটে ভর করে একবেলার খিদেকে ফাঁকি দিতে পারে। তবে এই পুরো গল্পে সবচেয়ে কম দামি বোধ হয় চা শ্রমিকের জীবন।
২
শিলিগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে এখন যেটা আকাশছোঁয়া বিলাসবহুল আবাসন ‘উত্তরায়ণ’, এক সময় সেখানেই চাঁদমনি চা বাগান ছিল। অধুনা শিলিগুড়ির বেশিরভাগ টিন এজারের কাছেই এই তথ্য অজানা। অবশ্যই জেনে ফেললেও এমসিকিউ ডেটাবেসের কোনো উল্লেখযোগ্য হেরফের হবে না। শুধু কয়েকজন পঞ্চাশোর্ধ উত্তরবঙ্গবাসী এখনো স্মৃতি হাতড়ে বলতে পারেন, ওখানে একটা চা বাগান ছিল।
আপাতত উন্নয়নের হড়পা বানে ভাসছে শিলিগুড়ি থেকে জয়গাঁও। আর দার্জিলিং-তরাই-ডুয়ার্স মিলিয়ে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে প্রায় এক ডজন চা বাগান। ধুঁকে ধুঁকে কোনমতে দিন গুজরান করছে আরও তিরিশটির মতো। বান্দাপানি, ঢেকলাপাড়া, লঙ্কাপাড়া, মুজনাই, কোহিনুর — প্রদীপের তলায় একে একে জমা হচ্ছে নিকষ অন্ধকার। কিন্তু ঔপনিবেশিক তথা স্বাধীনতাত্তোর ভারতের অন্যতম প্রধান অর্থকরী উৎস চা বাগানগুলোর এমন হতশ্রী দশা হলো কিভাবে? সেটা বুঝতে হলে চা ব্যবসার প্রাথমিক ইতিহাস টুকু জানা জরুরী।
অন্য যেকোনো কৃষিজ ফসলের ব্যবসার ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে ভারতে চা শিল্পের বিকাশের ইতিহাস অনেক বেশি জটিল এবং বিস্তৃত। কারণ প্রধানত দুটি। প্রথমতঃ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ঔপনিবেশিক ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে পরীক্ষামূলকভাবে চা চাষ শুরু হয়। তারপর মাত্র দুই শতকেরও কম সময় অত্যন্ত দ্রুত ব্যবসা বৃদ্ধি পেয়ে চা হয়ে উঠেছে ভারতের অন্যতম অপরিহার্য অর্থকরী কৃষিপণ্য। দ্বিতীয়তঃ ছোটনাগপুর মালভূমি এবং মধ্য ভারত থেকে বিপুল সংখ্যক আদিবাসী মানুষকে চা শ্রমিক হিসাবে চালান করায় চা বাগান সন্নিহিত অঞ্চলগুলি যেমন তরাই ডুয়ার্স ব্রহ্মপুত্র এবং বরাক উপত্যকার ভূমিপুত্রদের জনবিন্যাস বদলে গিয়ে এক নতুন জনসত্ত্বা তৈরি হয়েছে। এই বিষয়গুলি আমরা বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে সংক্ষেপে বোঝার চেষ্টা করব।
ভারতে চা চাষ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত চিনদেশই ছিল সারা বিশ্বের চায়ের প্রধান জোগানদার। ১৮৩৩ সালের আগে পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চীনের সঙ্গে চা ব্যবসায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব চালিয়ে ইউরোপের বাজার দখলে রেখেছিল। কিন্তু ১৮৩৩ সাল থেকে চীনের চা-বাণিজ্যে আরও বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় কোম্পানি ঢুকে পড়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তীব্র ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুখে ফেলে দিল। এই অবস্থায় একরকম বাধ্য হয়েই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে চায়ের নতুন উৎস খুঁজতে হচ্ছিল। ঘটনাক্রমে, এর মাত্র দশ বছর আগে ১৮২৩ সালে মেজর রবার্ট ব্রুস আসামের গভীর জঙ্গলে জংলি চা গাছের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের পায়ের নিচের জমি শক্ত করার জন্য এরপর ব্রিটিশ বেনিয়ারা কোমর বেঁধে নামলো। চা চাষের অনুকূল পরিবেশের খোঁজে হিমালয়ের পাদদেশে কয়েকটি জায়গায় (যেমন কুমায়ুন) পরীক্ষামূলক ভাবে চা চাষ শুরু হলো। এবং বিভিন্ন সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে কোম্পানি অচিরে এই সিদ্ধান্তে এলো যে, চা চাষের সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ উত্তর-পূর্ব ভারতের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা। ১৮৩৯ সালে আসাম টি কোম্পানি এবং টি অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতে প্রথম চা শিল্পের জয়যাত্রা শুরু হলো। ১৮৬১ সালের মধ্যে যে কোম্পানির উৎপাদন ক্ষমতা ঝড়ের গতিতে বেড়ে হল ১.২৫ মিলিয়ন পাউন্ড। একই সাথে লন্ডনের বাজারে নিজের সুগন্ধের দৌলতে চীনের চা-কে হারিয়ে দিয়ে তুমুল জনপ্রিয় হল ভারতীয় চা। ব্যাস! তারপর উপনিবেশে ব্যবসার ইতিহাসে বারবার যা হয় এবারও তাই হল। সাগর পারে ব্যবসা করে রাতারাতি ধনকুবের হওয়ার জন্য দলে দলে ইংরেজ উন্মত্তের মত পার্বত্য আসামের উপর আছড়ে পড়ল। ১৮৫৯ সাল থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত এই সাত বছর চললো আসামে চা বাগানের মালিক হওয়ার জন্য উদগ্র ইংরেজ ব্যবসায়ীদের বেপরোয়া জঙ্গল নিকেশ। যদিও ১৮৬৬ সালে ব্রিটেনের তীব্র আর্থিক মন্দার জেরে এই ফটকা বাজির উন্মত্ততায় কিছুটা লাগাম পরলো। ছোটখাটো বহু ভুঁইফোড় চা কোম্পানির অকাল মৃত্যু হল এবং প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলি টিঁকে গেল। এই পর্যায়ে টিঁকে যাওয়া বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীগুলির মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য স্কটিশ চা ব্যবসায়ী প্লেফেয়ার ডানকান এন্ড কোম্পানি। মন্দা কাটিয়ে ওঠার পর ইউরোপের বাজারে দ্রুত ব্যবসা এবং সুনাম দুইই বাড়তে থাকে ডানকান গোষ্ঠীর। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে চা ব্যবসা এবং ডানকান সমার্থক হয়ে যায়।
তবে এ পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা হল সবই আসাম চায়ের কথা। আমাদের রাজ্যে, ঠিক করে বলতে গেলে দার্জিলিঙে চা এসেছিল ১৮৪১ সালে। ডক্টর ক্যাম্পবেল তার দার্জিলিং-এর বাসভবনে সে বছর চীন দেশের কুশাং থেকে আনা একটি চা গাছের বীজ রোপন করলেন। সেই গাছ দার্জিলিং এর জল হওয়া আর মাটির গুণে গোকুলে কৃষ্ণের মতো তরতর করে বেড়ে উঠে চীনের বিশ্বজোড়া চা ব্যবসায় থাবা বসানোর স্বপ্ন গেঁথে দিল ব্রিটিশ বেনিয়াদের চোখে। এর পনেরো বছরের মধ্যে, ১৮৫৬ সাল থেকে দার্জিলিং পাহাড়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা উৎপাদন শুরু হলো। দার্জিলিং-এর লেবং এর কাছে ধোতরে চা বাগানই ছিল উত্তরবঙ্গের প্রথম চা বাগান। এরপর পাংখাবাড়ি, কার্শিয়াং, আলুবাড়ি হয়ে ১৯৪১ সাল নাগাদ দার্জিলিং পাহাড়ে চা বাগানের সংখ্যা দাঁড়ালো ৯১ টি। এই বাগান গুলিতে মালিক থেকে কর্মচারী সকলেই ছিলেন ইউরোপীয়। তবে একটা বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলেই নয়। এই বাগানগুলির মালিকদের অধিকাংশই যাকে বলা হয় প্লান্টার বা অন্য কোন বাগিচা শিল্পের মালিক, নিদেন পক্ষে বাগিচা শিল্প চালানোর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, এমনটা একেবারেই নয়। বরং এদের সিংহভাগই ছিলেন প্রাক্তন সামরিক অফিসার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সার্জেন এমনকি পশু চিকিৎসকও। অথচ কোন রকম পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই যেভাবে এরা ভারতের চা ব্যবসাকে আন্তর্জাতিক চা বাজারের কর্তৃত্বের সিংহাসনে বসালেন, ধ্রুপদী অর্থনীতির পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা সত্যিই মুশকিল।
ডুয়ার্সে চা বাগানের যাত্রা শুরু হয় আরো অনেক পরে। ১৮৭৪ সাল নাগাদ ডুয়ার্সে প্রথম চা বাগানের পত্তন হয়। আর আজকের তারিখে ডুয়ার্সের সর্বমোট চা বাগানের সংখ্যা ১৮১ টি, দার্জিলিং পাহাড়ে ৮৭ টি এবং তরাই অর্থাৎ শিলিগুড়ি লাগোয়া সমতলে ৩২ টি।
কিন্তু এতো গেলো সায়েব সুবোদের কথা। আর যাদের নিয়ে গান বাঁধা হলো, “চল মিনি আসাম যাবো” সেই সব বেনামী ইতিহাসকারদের কথা না বললে যে দুটি পাতা একটি কুঁড়ির ফ্লেভারটাই মাঠে মারা যায়!

৩
“কাজ ছেড়েছি দশ-বারো বছর হলো। আজকাল দিনের বেলাটা এই বাগানের আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করি, কাঠকুটো সংগ্রহ করি। বেশি দূরে কোথাও যাই না এই পাটকাপাড়া চা বাগানেই তো বলতে গেলে পুরো জীবনটা কাটিয়ে দিলাম।” — বলছিলেন বছর সত্তরের মাঙ্গিয়া ওঁরাও। আলিপুরদুয়ারের পাটকাপাড়া চা বাগানের বাতিল হয়ে যাওয়া চা শ্রমিক। এখনও শক্তপোক্ত গড়ন। তাঁর কততম ঊর্ধ্বতন পুরুষকে ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে চোরাচালান করা হয়েছিল এই কালাজ্বর আর ম্যালেরিয়ার জঙ্গলে, সে খবর তাঁরও অজানা। বললেন–“আমার তো জন্মই এই বাগানের কুলিলাইন ঘরে। একটু বড় হতেই পাতা তোলার কাজে ঢুকেছিলাম। কাজ করেছি, তা ধরো, চল্লিশ বছর তো হবেই। আরো বেশিই হবে। আমি কাজ ছাড়ার পরে আমার তিন ছেলেই পাতা তোলার কাজে ঢুকেছে। এই পাটকা পাড়া বাগানেই।”
মজুরির কথা ওঠায় হেসে বললেন–“আজকাল তো পাতা শ্রমিকদের অবস্থা অনেক ভালো। আমি যখন কাজ ছেড়েছি সে সময় দৈনিক মজুরি ছিল পঁয়ত্রিশ টাকা। ওই টাকাতেই তিন ছেলেকে বড় করেছি, মেয়েটার বিয়ে দিয়েছি মেচ পাড়ায়।” আমাদের বেয়াড়া কৌতূহলের আন্তরিক জবাব দিচ্ছিলেন আধা হিন্দি মেশানো মদেশীয় ভাষায়।
মদেশীয়। নামটা পাহাড়ের চা বাগানের নেপালি শ্রমিকদের দেওয়া। দার্জিলিং পাহাড়ের সমস্ত চা বাগানের প্রায় সব চা শ্রমিকই নেপালি। এরা এসেছিল বা বলা ভালো এদের আনা হয়েছিল পূর্ব নেপালের দারিদ্র পীড়িত তামাং, মগর, শানোয়ার, থাকালি, গুরুং, জাইনে ঠাকুরী ইত্যাদি উপজাতি থেকে। যদিও স্থানীয় লেপচা, ভুটিয়া, রাভা, ধীমল, থারু, রাজবংশী বা মেচরা কখনোই নিজেদের শতাব্দী প্রাচীন জীবনযাত্রা এবং আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে চা বাগানের কব্জায় আত্মসমর্পণ করেনি।
কিন্তু আসাম এবং ডুয়ার্সের চা বাগানের শ্রমিক সংগ্রহের ইতিহাস, দার্জিলিংয়ের চা বাগানগুলোর থেকে একেবারেই আলাদা। যে অমানুষিক প্রতারণায় একদল বিবেকহীন, অর্থলোভী মানুষ মধ্যভারত ও ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের অসংখ্য সহজ সরল আদিবাসীকে পশুর মত চোরাচালান করেছিল চা বাগান গুলোতে, তার বর্ণনা গল্পে-উপকথায়- ইতিহাসে কম বেশি আমরা সবাই জানি। আদিবাসী পাতা শ্রমিকদের একটা বড় অংশই চোরাচালান হয়ে এসেছিল মধ্যপ্রদেশের রেওয়া অঞ্চল থেকে। মধ্যদেশ থেকে আগত বলে নেপালি কুলিরা এদের নাম দেন মদেশিয়া। সেই থেকে মদেশিয়া সংস্কৃতির জন্ম।
ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি আসামে চা বাগান পত্তনের সময় প্রয়োজন পড়লো পর্যাপ্ত পাতা তোলার শ্রমিকের। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে চা-কর সাহেবেরা এই কাজে স্থানীয় আদিবাসীদের নিয়োগের পথে হাঁটলেন না। এমনিতেই যে কোন আদিবাসী সমাজ তাদের প্রচলিত জীবনযাত্রার বাইরে সহজে পা ফেলতে চায় না। তাছাড়া, সম্ভবত বিশ্বজোড়া উপনিবেশিক অভিজ্ঞতা থেকে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বভূমিতে আদিবাসীদের শোষণ করার থেকে ছিন্নমূল আদিবাসীদের শোষণ করা অনেক সহজ। তাতে অন্তত শোষণের ফলে উদ্ভূত বিক্ষোভ এবং গণবিদ্রোহের সম্ভাবনা অনেকটাই এড়ানো যায়। সুতরাং শ্বাপদের দৃষ্টি পড়ল সহজ শিকারের উপর। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের আদিবাসী সমাজ। এরা সরল, দরিদ্র এবং পরিশ্রমী। অতএব উল্লিখিত প্রথম দুটি গুণকে কাজে লাগিয়ে শুরু হলো বেলাগাম মানুষ পাচার। এই ব্যবস্থা এতটাই সংগঠিত ছিল যে, শিশুর মত সরল আদিবাসীদের ভুল বুঝিয়ে চোরাচালান দেওয়ার জন্য একটা স্থায়ী পেশার সৃষ্টি হল। এই সব দালালদের বলা হতো ‘আড়কাঠি’। এইসব আড়কাঠিদের কাজ ছিল ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের আদিবাসীদের বাজার হাটে নজর রাখা এবং অভাবী মানুষ দেখলেই বন্ধু সেজে কাজের লোভ দেখিয়ে চা বাগানের খপ্পরে এনে ফেলা। একটা কাজ আর দুটো ভাতের আশায় আদিবাসীরা চলে তো আসতো এই রাক্ষস পুরীতে, কিন্তু পৌঁছানোর পর বুঝতে পারতো একবার ঢুকলে এখান থেকে বেরোনো অসম্ভব। ১৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল টি প্লান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। এরাই শ্রমিক নিয়োগের নিয়মগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত। এই বছরে জারি করা ‘ওয়ার্কম্যান ব্রিজ অফ কন্ট্রাক্ট’ আইনের জেরে, কোন শ্রমিক চা বাগান ছেড়ে পালাতে চাইলে তার হাজতবাস অনিবার্য ছিল। উপরি হিসেবে যে নিদারুণ শারীরিক অত্যাচার ভোগ করতে হতো তার বর্ণনা পাওয়া যায় সনৎ কুমার দাসের বই (capital and labour in the Indian tea industry 1919) থেকে ক্যাপ্টেন ল্যাম্বের ডাইরি পর্যন্ত । অমানুষিক পরিশ্রম, আধপেটা খাবার আর অজানা রোগে অচিরেই মারা পড়তো আসামে পাচার হয়ে আসা এই আদিবাসীদের একটা বড় অংশ। কেমন ছিল এই নির্বান্ধব অচেনা কারাগারে তাদের মৃত্যুর খতিয়ান? একটা হিসাব দিলে ছবিটা কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে।
‘১৮৬৩ সালের পয়লা মে থেকে ১৮৬৬ সালের পয়লা মে অর্থাৎ এই তিন বছরে আদিবাসী এলাকা থেকে ৮৪,৯১৫ জন মানুষকে চালান করা হয়েছিল এর মধ্যে ৩১,৪৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল।’– (history of Indian tea industry/ GRIFITTO)
চা-কর সাহেবদের চোখে শ্রমিকদের মৃত্যুর হিসেব হতো আদতে আর্থিক ক্ষতির মাপকাঠিতে, কারণ আড়কাঠিরা চাকুরীজীবী ছিল না। তাদের চা-শ্রমিক পিছু কমিশন দিতে হতো।
হয়তো সেই কারণেই,আসামের বেশ কিছুটা পরে, ডুয়ার্সে চা বাগান পত্তনের সময় শ্রমিকদের মৃত্যুর হার তুলনামূলক ভাবে সামান্য কম ছিল। এমনকি ডুয়ার্সের চা শ্রমিকদের কোনো বাধ্যতামূলক চুক্তিপত্রেও সই করতে হতো না। যদিও অত্যাচারের মাত্রার বিশেষ হেরফের হয়েছিল বলে জানা যায় না।
১৮৮১ সালে রেল চলাচল শুরু হওয়ার পর আরো মসৃণ হয়ে ওঠে এই চোরাচালান এবং স্বাধীনতার প্রাক মুহূর্ত ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত একটানা অবাধে চলতে থাকে এই মানুষ পাচারের কারবার।
৪
স্বাধীনতার পর চা বাগান গুলির চরিত্রে এক বিরাট আর অভাবনীয় পরিবর্তন এলো। এ কথা সত্যি যে, ব্যবসায় অধিক উৎপাদন এবং বেশি মুনাফার লোভে ইংরেজ মালিকরা চা শ্রমিকদের উপর অকথ্য অত্যাচার করতো। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুনাফার লোভে তারা বাগানের পরিচর্যা এবং উৎপাদনশীলতার সাথে আপোষ করতো না। সুতরাং উৎপাদনের পরিমাণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের গুণমান কোনটাই নিচের দিকে নামেনি। ফলে সমস্ত অত্যাচার সত্ত্বেও, পাতা শ্রমিকদের কখনো কাজ হারিয়ে বেকারত্বের সম্মুখীন হতে হয় নি। স্বাধীনতার পর, যে কোন উপনিবেশের মতই, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ইংরেজদের ছেড়ে যাওয়া চা বাগানগুলির মালিকানা হাতে পেল এবং মাত্র অর্ধ শতকের মধ্যে বাগানগুলির উৎপাদনশীলতা এবং গুণমানের অধঃপতন হলো চোখে পড়ার মতো। কারণ আর কিছুই নয় সহজ লাভের আশায় চা বাগিচার পরিচর্যা দিকটিকে চরম অবহেলা করা। অধিকাংশ অপদার্থ বাগান মালিক চা বাগানের পরিচর্যার খরচ বাঁচাতে ‘প্ল্যান্টেশন অ্যাক্ট’কে বুড়ো আঙ্গুল দেখায়। সাধারণভাবে ৫০ বছরের বেশি বয়সী চা গাছকে বাণিজ্যিকভাবে অনুৎপাদক ধরা হয়। একটু চোখ কান খোলা রাখলেই দেখা যাবে, অধিকাংশ চা বাগান যারা লোকসানের অজুহাত দেখিয়ে বছরের অর্ধেক দিন চা শ্রমিকদের মজুরি বন্ধ রাখে, সেইসব বাগানের অধিকাংশেরই চা গাছগুলির বয়স নিদেন পক্ষে ৬০ বছর, কোথাও কোথাও ৭৫ থেকে ৮০ বছর। যার ফল ভুগতে হয় শেষ অবধি প্রান্তিক চা শ্রমিকদের। এ বিষয়ে গোয়েঙ্কাদের চা বাগানগুলির (স্বাধীনতার পূর্বে ডানকানস ব্রাদার্স লিমিটেড) লোকসানের কুখ্যাতি তো ভারত জোড়া। ডানকানের স্বীকৃতি অনুযায়ী, তাদের কর্মী সংখ্যা প্রায় ১৯,৫০০ এবং পাতা তোলার মরশুমে আরো কিছু অস্থায়ী কর্মীও নিয়োগ করা হয়। মালিকপক্ষের মর্জি মাফিক যখন তখন বাগান বন্ধ রাখলে কাজ হারিয়ে অথৈ জলে পড়েন এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিক।
প্রসঙ্গত, যে কোন অজুহাতে বাগানে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া উত্তরবঙ্গের বেশকিছু চা বাগানে একটি আকছার ঘটনা। একটা আশ্চর্য উদাহরণের দিকে চোখ রাখা যাক। ২০১৯ সালের ৩রা এপ্রিল, পাতা তোলার ভরা মরশুমে, আচমকা কারখানার গেটে লক আউটের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয় আলিপুরদুয়ারের ‘চুয়াপাড়া চা বাগান’। কারণ হিসাবে বাগান কর্তৃপক্ষ জানায়, চা শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা ১২ কিলোমিটার দূরের হাইস্কুলে পড়তে যাওয়ার জন্য স্কুল বাসের দাবি করছে। বাগান কর্তৃপক্ষ আরো জানায়, স্কুলের ছেলেমেয়েদের এই দাবিতে নাকি বাগানের কর্মসংস্কৃতির প্রচন্ড অবনতি হয়েছে! সুতরাং চুয়াপাড়া চা বাগানের প্রায় ২৬০০ স্থায়ী ও অস্থায়ী চা শ্রমিককে গভীর আতান্তরে ফেলে, কারখানায় লকআউট নোটিশ ঝোলাতে দু’বার ভাবেনি বাগান কর্তৃপক্ষ!
বিভিন্ন সময়ে আঙুল উঠেছে ‘দাগাপুর’ চা বাগানের দিকেও। স্বাধীনতার আগে এই বাগানটিই ‘পঞ্চানই’ চা বাগান নামে খ্যাত ছিল, আন্তর্জাতিক বাজারে যার চায়ের গুণমান ছিল প্রথম সারিতে। দার্জিলিং পাহাড়ে ‘অ্যালকেমিস্ট’এর চা বাগান গুলির অচলাবস্থাও অব্যাহত।
তবে ব্যতিক্রমও আছে। আলিপুরদুয়ারের মাঝের ডাবরি চা বাগানটি ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘রংপুর টি অ্যাসোসিয়েশন’র অন্তর্গত। দেশভাগের পর রংপুর জেলা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বাগানটি ভারতের অংশে পড়ে। স্বাধীনতার পরেও মাঝের ডাবরি বাগানটি উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে এবং দেশের বাজারে তাদের চায়ের সুনামও যথেষ্ট। বাগান এবং কারখানা মিলিয়ে কর্মী সংখ্যা কমবেশি দেড় হাজার, যাদের একাংশ বংশ পরম্পরায় ধর্মান্তরিত আদিবাসী খ্রিস্টান।তাদেরই একজন, কুলি বস্তির ঠিকা শ্রমিক জন মুর্মু। আলাপ চলছিল কোনো এক বুধবারে, বাগানের ছুটির দিনে। বছর পঁয়ত্রিশের জন দুই বাচ্চাকে সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসিয়ে স্কুল থেকে বাড়ি নিয়ে ফিরছিলেন। জাতীয় সড়কের দু’ধারে বিস্তৃত এই চা বাগান থেকে আমাদের বেরোনোর রাস্তা চিনিয়ে দিতে দিতে জানালেন, আজকাল কুলি বস্তিতে মশা মাছির প্রকোপ অনেক কম। নিয়মিত ওষুধ স্প্রে করা হয়। মজুরির কথায় বললেন, গত কয়েক মাস আগেও বাগান কর্মীদের দৈনিক মজুরি ২০২ টাকা ছিল, এখন এক লপ্তে ৩০ টাকা বেড়ে ২৩২ টাকা হয়েছে।
৫
চা শ্রমিকদের মজুরীর বিষয়টা বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের রহস্য উদ্ধার অথবা তৃতীয় বিশ্বের শিশুশ্রম অবলুপ্তির মতো। এসব নিয়ে যত গবেষণা পত্র আর নিউজ প্রিন্ট খরচ হয়েছে, কাজের কাজ তার শতকরা দশ ভাগও হয়নি। চা শ্রমিকদের মজুরির বিবর্তন এবং বিবর্ধন নিয়ে তথ্য ঘাঁটতে গিয়ে যেটুকু যা পেলাম তাতে বুঝলাম, চা শ্রমিকদের মজুরির ব্যাপারটা মালিকপক্ষ আর রাষ্ট্রের তরফ থেকে আদতে একটা কুৎসিত তামাশা ছাড়া কিছু নয়। নথি অনুসারে, মোটামুটিভাবে স্বাধীনতার আশেপাশের সময়কালে চা শ্রমিকদের মজুরি ছিল চার আনা, মহিলাদের তিন আনা এবং কিশোরদের ছ’ পয়সা। ডুয়ার্সের বিভিন্ন বাগানের বয়স্ক শ্রমিকদের সাথে আলাপচারিতায় যেটুকু জানা গেল, এই শতকের গোড়ার দিকেও চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ছিল ৩৫ থেকে ৪০ টাকা। ২০০৭ সাল নাগাদ যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ডুয়ার্সে ৯৫ টাকা এবং দার্জিলিংয়ের ৯৭ টাকা, অন্যান্য প্রদেয় সুবিধাগুলি (ফিঞ্জ বেনিফিট) সহ। (ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন, ২০০৭)
এরপরের দেড় দশকে(২০২২) চা শ্রমিকদের এই মজুরি মোটামুটি দ্বিগুণ হয়ে পৌঁছেছে কমবেশি ২০০ টাকায়, যা মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় নেহাতই হাস্যকর। তাছাড়া মজুরীর এই অঙ্কও সর্বত্র সমান নয়। চলতি বছরে পাতা তোলার মরশুমের শুরুতে দার্জিলিং, ডুয়ার্সের বেশিরভাগ বাগানে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় চা শ্রমিকদের মজুরি ২০৫ টাকা হলেও বারাক উপত্যকার বাগান গুলিতে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ছিল ১৮৩ টাকা। একই কাজে সমমজুরির দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন চালাচ্ছেন বারাক উপত্যকার চা শ্রমিকরা।
লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, চা ব্যবসা একটা সংগঠিত শিল্প হলেও মজুরির এই অঙ্কটা সরকার স্বীকৃত দৈনিক ন্যূনতম মজুরির অর্ধেকেরও কম।
নীচের পরিসংখ্যানে চা বাগানের সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি সংগঠিত শিল্পের অদক্ষ শ্রমিকদের তুলনা দেওয়া হলো।

কিন্তু কেন চা শ্রমিকের মজুরি বাড়াতে এত অনীহা মালিকপক্ষের? মজুরি না বাড়ানোর পক্ষে কি কি যুক্তি হাজির করেন চা বাগান মালিকেরা? এই প্রসঙ্গে “চা বাগান সংগ্রাম সমিতি’র সমীক্ষা থেকে উঠে আসা বক্তব্যটুকুই এখানে হুবহু তুলে দিলাম।
“যে নির্দিষ্ট বিষয়টি আমাদের চা বাগান মালিকরা বিশ্বাস করাতে চাইছে , সেটি হল — মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাবদ খরচ অত্যন্ত বেশি হওয়ায় ভারতে চায়ের উৎপাদন ব্যয় খুবই বেশি। যা ভারতীয় চা শিল্পকে দেশের এবং বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দিচ্ছে। তাদের হিসাব অনুযায়ী উৎপাদন খাতের মোট খরচের ৫৫% শ্রমিকদের মজুরিতেই চলে যায়। পাশাপাশি মালিকরা এটাও বলে যে বর্তমান নগদ মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাবদ শ্রমিকরা যা পায়, তা তাদের উৎপাদনশীলতার থেকে অনেক বেশি এবং তার ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে।”–(চা শিল্পের সংকট/তামস রঞ্জন মজুমদার) প্রশ্ন হলো, চা শিল্প তথা চা ব্যবসা কি সত্যি সঙ্কটের মুখে? যে কোন ব্যবসার অর্থনৈতিক সাফল্য নির্ভর করে তার লাভজনক বিক্রির পরিমাণ এবং ব্যাপ্তির উপর। দেশের বাজারে চা শিল্পের আকাশ ছোঁয়া ব্যবসার একটা আবছা ধারণা তো আমরা এই প্রবন্ধের ভূমিকাতেই দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এবারে ভারতীয় চায়ের আন্তর্জাতিক বাজারের দিকে একবার ইতিউতি চোখ রাখা যাক।
আজকের দিনে ভারতবর্ষ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম চা উৎপাদক দেশ। প্রসঙ্গত, বিশ্বের বৃহত্তম চা উৎপাদক দেশ চীন। সে দেশে চায়ের বার্ষিক গড় উৎপাদন চব্বিশ লক্ষ টন। ভারতে চায়ের বার্ষিক গড় উৎপাদন নয় লক্ষ টনের অধিক। যার মধ্যে বার্ষিক গড়ে দুই লক্ষ টনেরও বেশি চা লাভজনক মুল্যে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করা হয়। বাকি সাত লক্ষ টনের বেশি চায়েরও আভ্যন্তরীণ বাজার যথেষ্ট লাভজনক এবং চাহিদাও বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর। কিন্তু ভারতীয় চায়ের এই বিপুল আন্তর্জাতিক বাজার একদিনে গড়ে ওঠেনি।
ভারতের চা রপ্তানির ইতিহাস খুঁড়লে দেখা যায় যে, ১৮৩৮ সালে ৩৫০ পাউন্ড চা কলকাতা বন্দর থেকে লন্ডনের চা নিলাম কেন্দ্রে পাঠানোর মাধ্যমে ভারতীয় চায়ের আন্তর্জাতিক জয়যাত্রার সূত্রপাত। পরের চার দশকে এই রপ্তানির পরিমাণ বিপুল বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮০ সালে ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ডে পৌঁছালো। সেই সময় আন্তর্জাতিক চা-বাণিজ্যে চীন ছিল সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারী দেশ। ১৮৮৯ সালে ভারত চীনকে ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে সর্বোচ্চ রপ্তানিকারী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেল। সে বছর আন্তর্জাতিক চায়ের নিলাম কেন্দ্রে চীনের পাঠানো চায়ের পরিমাণ ছিল ৬১ মিলিয়ন পাউন্ড এবং ভারত পাঠাতে পেরেছিল ৯৬ মিলিয়ন পাউন্ড। এরপর সমগ্র বিংশ শতাব্দী জুড়ে চীনকে পিছনে ফেলে ভারত ছিল বিশ্বের সর্বোচ্চ চা উৎপাদনকারী দেশ। এমনকি বিভিন্ন মহল থেকে যে সময়টিকে ‘ভারতীয় চা শিল্পের ভয়াবহ মন্দা’ বলে অভিহিত করা হয়, সেই ২০০০ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সময়কালেও আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় চায়ের দাপট ছিল যথেষ্টই।
নীচের পরিসংখ্যানটি ‘টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া’র’ সোউজন্যে প্রাপ্ত

ইদানিং কালে প্রথম বিশ্বের দেশগুলিতে ভারতের চা রফতানির কয়েকটা খতিয়ান এই ছবিটাকে আরেকটু স্পষ্ট করতে পারে। দার্জিলিংয়ের মকাইবাড়ি বাগানের বিশেষ চা ২০১৪ সালের আন্তর্জাতিক নিলামে জাপান, ব্রিটেন এবং আমেরিকার বাজারে কেজিপ্রতি ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছিল। আজকের তারিখ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় চায়ের এটাই সর্বোচ্চ দাম।
সদ্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া দুটি পরস্পর প্রতিবেশী দেশ রাশিয়া এবং ইউক্রেন ভারত থেকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ চা আমদানি করে। রাশিয়াতে বছরে ৪ কোটি ২০ লক্ষ কিলোগ্রাম আসাম চা রফতানি করা হয়। আর ইউক্রেনে রফতানি করা হয় ৩০ লক্ষ কিলোগ্রাম আসাম চা। সব মিলিয়ে শুধু এই দুটি দেশ ভারত থেকে বছরে মোট সাড়ে চার কোটি কিলোগ্রাম চা ক্রয় করে থাকে।
উপরের হিসাবগুলি বিবেচনায় আনলে, ‘চা শিল্প সংকটে’ কিংবা ‘চা ব্যবসা যথেষ্ট লাভজনক নয়’ — এইসব বয়ানের আদৌ কোন সারবত্তা থাকে কি?
৬
“চা শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে আন্দোলনের প্রেক্ষিতটাই জটিল হয়ে গেছে গত কয়েক বছরে।” — মুখোমুখি আলাপচারিতায় বলছিলেন উত্তরবঙ্গের অধিকার আন্দোলনের কর্মী অর্ঘ্য মিত্র। কথা হচ্ছিল আলিপুরদুয়ারের ঘরোয়া পরিবেশে। আমাদের জিজ্ঞাসু চোখের জবাবে পরিস্থিতিটা বোঝাতে যা বললেন, তার সারমর্ম এক কথায় বঞ্চনার ইতিহাসকে ব্যবহারের রাজনীতি। তাঁর কথায়, চা শ্রমিকদের আন্দোলনের সংগঠনগুলিতে শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা ছাড়াও প্রধানত আছেন উত্তরবঙ্গের বামপন্থী গণ আন্দোলনের কর্মীরা এবং বিভিন্ন অধিকার কর্মীরা। এইসব আন্দোলনের মঞ্চে শাসকদলের কর্মীরা নেই বললেই চলে, তাদের থাকার কথাও নয়। কিন্তু এ রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের নীতি অনুসারে রাজ্যের সর্বত্র যে সুষ্ঠ পরিকল্পনাহীন অনুদান এবং ডামাডোলের রীতি চলছে চা বাগানও তার বাইরে নয়। ২০২০ সালের রাজ্য বাজেটে চা বাগানে গৃহহীন শ্রমিকদের জন্য ‘চা সুন্দরী’ আবাসন প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছিল। যে পাঁচটি চা বাগানে সরকারিভাবে বসতবাড়ি তৈরি করার জন্য প্রস্তাবিত তার মধ্যে রয়েছে লঙ্কাপাড়া, ঢেকলাপাড়া, তোর্সা, মুজনাই এবং রহিমপুর।
চলতি বছরের ৮ই জুন উত্তরবঙ্গের হাসিমারায় এক জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিকদের বর্তমান দৈনিক মজুরি একলপ্তে ১৫% বাড়িয়ে ২০২ টাকা থেকে ২৩২ টাকা ঘোষণা করেন। স্বভাবতই এই সব উপঢৌকন পেয়ে হতদরিদ্র সরল চা শ্রমিকরা যারপরনাই সন্তুষ্ট। এমতাবস্থায় জাতীয় শ্রমদপ্তর ঘোষিত ন্যূনতম দৈনিক মজুরীর দাবিতে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করা কার্যত অসম্ভবের নামান্তর। তাছাড়া মজুরি বৃদ্ধির দাবি করার ক্ষেত্রে কিছু নৈতিক সমস্যাও আছে সংসদীয় বামপন্থীদের। এ রাজ্যে বামপন্থী শাসনকালে যেখানে বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি হতো বড়জোর দেড় থেকে দুই টাকা, সেখানে একলাফে তিরিশ টাকা মজুরি বৃদ্ধির পর চা শ্রমিকরাই বারবার তুলনা টানছেন বাম আমলের সঙ্গে।
শ্রমিকদের একজোট হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে আরও। জাতিসত্তার কারণে পাহাড়ের অধিকাংশ নেপালী চা শ্রমিকই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার বা বলা ভালো গোর্খাল্যান্ডের দাবির সমর্থক। কিন্তু ছিন্নমূল হওয়ার কারণে মদেশিয়া চা শ্রমিকদের জাতিসত্তার বোধ ততটা তীব্র নয় এবং গোর্খাল্যান্ডের দাবি থেকে তাদের প্রাপ্তির কিছু নেই। সুতরাং গোর্খা জনমুক্তি আন্দোলনের প্রশ্নে চা শ্রমিকদের মধ্যে একটি স্পষ্ট বিভাজন রয়েছে।
কিন্তু হাল আমলে চা শ্রমিকদের আন্দোলনের এমন ছন্নছাড়া দশা হলেও শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে লড়াইয়ের ইতিহাসটা তো আজকের নয়।
ডুয়ার্সের চা শ্রমিকদের অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য প্রথম কমিশন বসেছিল ১৯১১ সালে। আর ১৯৭৪ সালে শ্রমিকদের উদ্যোগে এবং সরকারি সহযোগিতায় তৈরি হলো এদেশের প্রথম চা বাগান কো-অপারেটিভ সোসাইটি। প্রথম কমিশন থেকে প্রথম কো-অপারেটিভ সোসাইটি পর্যন্ত আসতে স্বাধীন-পরাধীন মিলিয়ে ভারতবর্ষের লেগে গেল তেষট্টিটা বছর!
কিন্তু এসব তথাকথিত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেরও বহু আগে, ১৮৮৭ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সম্পাদক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ব্যক্তিগত উদ্যোগে সরেজমিনে তদন্ত করে আসামের চা বাগানগুলিতে শ্রমিকদের উপর নৃশংস অত্যাচারের কাহিনীকে সভ্য সমাজের কাছে বেআব্রু করে দিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করার জন্য তিনি ছদ্মবেশে দিনের পর দিন চা বাগিচায় কুলি বস্তিতে আত্মগোপন করে থেকে শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তার সংগৃহীত অভিজ্ঞতা ১৮৮৭ সালের ‘সঞ্জীবনী’ এবং ‘বেঙ্গলি’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলে কলকাতা সহ লন্ডনের সভ্য সমাজে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। চা শ্রমিকদের আন্দোলনের ইতিহাসে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীকেই পথিকৃৎ বলা যায়। ঠিক তার পরের বছর অর্থাৎ ১৮৮৮ সালে ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন অসম ও উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের অবস্থা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করে লিখেছিলেন সেই বিখ্যাত গ্রন্থ ‘কুলিকাহিনী’। যদিও এসবই চা বাগানের ইতিহাসের প্রথম দিকের কথা এবং মনে রাখা দরকার দ্বারকানাথ বা রামকুমাররা ছিলেন সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত কলকাতা শহরের বাসিন্দা। যেমন পরবর্তীকালে শ্রমিক আন্দোলনগুলিও প্রধানত পরিচালিত হয়েছে শ্রমিক সমাজের বাইরে থেকে আসা প্রশিক্ষিত রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ছত্রছায়ায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বিরাট নির্যাতিত শ্রমিক সমাজের ভিতর থেকে তেমনভাবে কোন আওয়াজ উঠে এলো না কেন? কিন্তু দীর্ঘ শতাধিক বছর ধরে এক বিপুল জনগোষ্ঠীর মানুষকে ক্রমাগত শোষণ আর অত্যাচার করে তাদের বোধ শূন্য করে দিলে এমনটাই স্বাভাবিক নয় কি?
তবু ব্যতিক্রম থাকে। ১৯৮১ সালের ১৪ই জুন গৌর কিশোর ঘোষের সম্পাদনায় তৎকালীন ‘আজকাল’ পত্রিকায় প্রকাশিত হলো একজন চা শ্রমিকের লেখা দীর্ঘ চিঠি। লেখক জলপাইগুড়ির ‘সোনালী চা বাগানে’র পাতা শ্রমিক সাইমন ওঁরাও। চিঠি না বলে তাকে চা শিল্পের সমবায় আন্দোলনের জীবন্ত দলিল বলাই সঙ্গত। চৌদ্দ বছর পর, ১৯৯৫ সালে সেই চিঠি পুনঃপ্রকাশ করেন লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘বর্তিকা’র জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। আজও যতবার চা শ্রমিকদের আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা ওঠে, সাইমনের চিঠি ভূত হয়ে ফিরে ফিরে আসে। আর এইসব দীর্ঘ ধারাবাহিকতার উত্তরাধিকারী আজকের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানবাঅধিকার কর্মীরা কিংবা ‘চা বাগান সংগ্রাম সমিতি’র মত সংগঠনগুলি।
কিন্তু নিজেদের অধিকার আদায়ের প্রশ্নে আজকের চা শ্রমিকরা কি সত্যিই বিভ্রান্ত? এইসব কঠিন কঠিন নাগরিক প্রশ্নের বোঝা নিজেদের মাথায় চাপিয়ে এক বৃহস্পতিবারের ভরদুপুরে হাজির হয়েছিলাম আলিপুরদুয়ারের পাটকাপাড়া চা বাগানে। দলে দলে পুরুষ আর মহিলা শ্রমিক দুপুরের বিরতিতে খেতে ফিরছিলেন যার যার ঘরে। সংখ্যায় মহিলারাই বেশি, তাদের মধ্যেই মনে হল মাঝবয়সী দুজনের তাড়া একটু কম। দুটি স্কুলের বান্ধবীর মত খোশ মেজাজে গল্প করতে করতে হেঁটে আসছে বাগানের মাঝ বরাবর। গায়ে পড়ে আলাপ করে জানলাম একজনের নাম লছমি, অপর জন সোমারি। সম্ভবত সোমবারে জন্ম হওয়ায় এ হেন নামকরণ। কাজকর্মের পরিস্থিতি জিজ্ঞাসা করায় জানালেন আগের আগের চেয়ে এখনকার পরিস্থিতি অনেক ভালো। আগে তো শীতের তিন মাস বাগানের কাজ বন্ধ থাকতো। চা ফুল আর মেটে আলু সংগ্রহ করে খিদের মোকাবিলা করতে হতো তখন। আজকাল শীতের মরশুমেও অর্ধেক মজুরিতে এক বেলা বাগান পরিচর্যার কাজ চালু থাকে। খানিকটা সন্দিগ্ধ হয়েই প্রশ্ন করলাম, ‘তবে যে কানাঘুষো শুনেছি মাসখানেক আগে এই পাটকাপাড়া বাগানেরই মহিলা শ্রমিকেরা মজুরি নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন?’ দুজনেই সমস্বরে জানালেন, ‘হয়েছিল তো! কিন্তু এখন ওসব মিটমাট হয়ে গিয়েছে। সামনেই করম পরব। পাতা কারখানার সাহেব আর বাবুরা বেশ ভালো চাঁদা দিয়েছে এ বছরের করমে। উৎসবের আয়োজন যা করার সেসব কুলি বস্তির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই করছে। বড়দের সময় আছে নাকি?’
আমি আরো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তাহলে কি আপাতত আপনাদের তেমন কোনো সমস্যা নেই?’
সোমারি হাসিমুখে বললেন, ‘তা থাকবে না কেন? কোনো না কোনো সমস্যা তো লেগেই থাকে বছরভর। কিন্তু সে তো চা বাগানে সাপ আর বিচ্ছুও থাকে। তাতে কি?’ তারপর লছমির হাত টেনে বললেন, ‘যাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে। খেয়ে এসে দুপুরের কাজ ধরতে হবে…’
আমাদেরকে দিগন্তবিস্তৃত এই চা বাগানের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে ওরা দলে দলে বাগান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সেই সমবেত নিষ্ক্রমনের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছিলাম আমাদের আর ওদের মধ্যে ‘জিডিপি’, ‘চায়পে চর্চা’, ‘অধিকার আন্দোলনে’র মতো অনেকগুলো দুর্বোধ্য দেওয়াল আছে। সারা জীবন মাথা খুঁড়লেও আমার পক্ষে সেইসব দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে লছমি আর সোমারিদের সুখ-দুঃখের অন্দরমহলে প্রবেশ করা হবে না।

আরও পড়ুন – সৌন্দর্যশাস্ত্র ও দলমিলিয়ে দেওয়ালচিত্র রাজনগর, বীরভূম