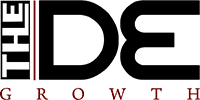ভারতবর্ষ: ২০৫০
০
প্রথমে ভেবেছিলাম “বিদ্ধস্ত প্রজাতন্ত্র” (The Republic of Disaster), বা এরকম কিছু নাম দিয়ে একটা বই প্রকাশ করবো। বইয়ের বিষয়বস্তু ২০৫০এর ভারতবর্ষ (India: 2050)। আজ থেকে ২৮/৩০ বছর পরে এই দেশের যে অবস্থা হতে যাচ্ছে তা নিয়ে একধরনের সত্য-কল্পনা। অর্থাৎ, আজকের সত্যের নিরিখে ভবিষ্যত ভারতভূমির এক কাল্পনিক কথাছবি।
এখানে সত্য বলতে আমি অবশ্যই বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা বলছি। যেমন পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে, এটা সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য। তার ফলে সমুদ্র স্ফিত হচ্ছে, এটা সত্য। সমুদ্রের বর্ধিত জলস্তর ক্রমে তটভূমি গ্রাস করছে, এটা সত্য। সমুদ্রে নিম্নচাপের সংখ্যা বাড়ছে এটা সত্য। সেই নিম্নচাপের ফলে প্রবল ঘূর্ণিঝড় দুদিন অন্তর অন্ধ্র, উড়িষ্যা, পশ্চিম বঙ্গের উপকূলে আছড়ে পড়ছে এটা সত্য।
বিজ্ঞানের এই সত্য আজ আর কোনো দূরবর্তী সত্য নয়। বিজ্ঞানের বিমূর্ত গন্ডি ছাড়িয়ে তা আজ আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। যেমন বছরে কয়েকটি ঘূর্ণিঝড় আজ উপকূলবর্তি মানুষজনের অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাগরদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, গোসবার মানুষের কাছে আয়লা, হুদহুদ বা ফোনি কোনো টেলিভিশনে দেখা চোখধাঁধানো সংবাদপণ্য (spectacle) নয়। তাদের নিয়ম করে বছরে কয়েকবার ঘরবাড়ি ছেড়ে পরিবারসমেত সরকারি রিলিফক্যাম্পে গিয়ে উঠতে হয়। তাদের জমি নোনা জলে ভরে যায়। ফলে চাষ করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। তাদের ছেলেরা কাজের খোঁজে দিল্লি, গুজরাট বা কেরালাতে পাড়ি দেয় ঠিকে শ্রমিক হিসেবে। তাদের মেয়েদের অনেকে ঠিকে ঝিয়ের কাজ করতে আসে কলকাতায়। আর যাদের কপাল আরো খারাপ তাদের স্থান হয় সোনাগাছিতে।
ছোটবেলায় আমরা পড়েছিলাম “আষাঢ় শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষাকাল”। আমাদের মত শহুরে লোকেদের বাংলা মাসের হিসেব করতে হয় ইংরেজি মাস দিয়ে। ১৫ই এপ্রিল পয়লা বৈশাখ। তারপর দুই মাস গ্রীষ্মকাল। অর্থাৎ, ১৫ই এপ্রিল থেকে ১৫ই মে হয়ে ১৫ই জুন পর্যন্ত। ১৫ই জুন থেকে এই বাংলায় বর্ষা নামার কথা। কত বছর হলো বাঙালি আষাঢ় মাসে বৃষ্টি দেখেনি। জলবায়ু বিজ্ঞান বলছে মৌসুমী বায়ু বিপর্যস্ত। এই বৈজ্ঞানিক সত্য এতদঅঞ্চলের কৃষকেরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে তাদের জীবন দিয়ে। বর্ষার বৃষ্টি তার সমস্ত ছন্দ হারিয়েছে। যে ছন্দের সাথে যুগযুগধরে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের চাষবাস, জীবনজিবিকা, পালাপার্বন ও গ্রামসংস্কৃতি।
১
গত দুদশক ধরে কলেজে পরিবেশবিদ্যা পড়াচ্ছি। তাও আবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত শহর ডায়মন্ড হারবারে। যেখানে কিনা বছরে দুতিনবার ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ে। যেখানে কিনা সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ। তবু এখানকার ছাত্রছাত্রীদের দেখে অবাক না হয়ে পারিনা।
প্রতিবছর যখন ক্লাস শুরু হয় আমি দক্ষিণ
চব্বিশ পরগনার সম্ভাব্য পরিবেশ বিপর্যয়ের ছবিটি বেশ নাটকীয়ভাবেই ওদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করি। করে আসছি এত বছর ধরে। তবু কোনো হেলদোল নেই। ওদেরকে বলি যে এই ডায়মন্ড হারবার শহরের আয়ু আর খুব বেশিদিন নেই। ওদেরকে বলি যে শুধু ওরা কেন, গোটা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আপামর জনসাধারণ আগামী দুতিন দশকের মধ্যে পরিবেশ উদ্বাস্তু হতে চলেছে। খুব বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করি যে কিভাবে ম্যানগ্রোভ অরণ্য, যা এই বদ্বীপকে রক্ষা করতো তা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিভাবে এই বদ্বীপটা ধীরে ধীরে বসে যাচ্ছে। কিভাবে চাষের জমিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে ভৌমজলস্তর বহু নিচে নেমে গেছে।
কিভাবে মাটির নিচ দিয়ে সমুদ্রের নোনা জলে চুইয়ে ঢুকছে। অর্থাৎ, ছবিটা হচ্ছে, ২০৫০ শাল নাগাদ সাতপুরুষের ভিটেমাটি হারানো লক্ষ লক্ষ গৃহহীন মানুষের মিছিলের ছবি। সেই সব উদ্বাস্তু জনতার খাদ্য নেই, কারণ একইসাথে নেমে আসবে কৃষিতে বিপর্যয়। তার থেকেও বড় কথা, সেই সব নিরন্ন মানুষের পানিয় জলও থাকবেনা। বিজ্ঞান বলছে যে ২০৩০ শালে আমাদের পানিয় জলের যে চাহিদা দাঁড়াবে তার অর্ধেক জলের সংস্থানও এদেশে নেই।
এরকম একটা ছবি, তবু কোনো হেলদোল নেই। যদিও কিছু ছাত্রছাত্রী থাকে যারা সংবেদনশীল। তারা প্রতিবছরই আগ্রহ প্রকাশ করে যে তারা কিছু করতে চায়। পরিবেশ আন্দোলনে সামিল হতে চায়। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায় বা গঠনমূলক কিছু করতে চায়। ব্যাস ওই অবধি। পড়াশোনা চলে, তার মাঝে আলাপ আলোচনা চলে। তার মধ্যে পরীক্ষা এগিয়ে আসে। তখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রজেক্ট, ইন্টারনাল এসেসমেন্ট ইত্যাদি। পরীক্ষা হয়ে যায়। দেখাসাক্ষাৎ কমে আসে। তার সাথে সব উৎসাহ ঝিমিয়ে পরে। প্রতিবছর ওই একই ছবি।
আমি গভীরভাবে ভাবি সমস্যাটা কোথায়?
ছাত্রছাত্রীদের সাথে অধ্যাপক হিসেবে আমার যে সম্পর্ক তা মূলত প্রাতিষ্ঠানিক, অর্থাৎ ক্ষমতার সম্পর্ক। ওদের দায় পরীক্ষা পাস করবার। সেখানে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বর আমার হাতে। প্রজেক্টে ৩০, ইন্টারনালে ১০, আর আটেন্ডেন্ন্সে ১০। এই সব মিলিয়ে ৫০ নম্বর। সোজা কথা? কেন ওরা আমার হ্যাঁযে হ্যাঁ মেলাবেনা?
তাছাড়া আমার বোঝা উচিত ছিল যে পৃথিবীর তাবর বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের দর্শনে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, সমাজবিজ্ঞানে বা সাংস্কৃতিক বিদ্যায় গুছিয়ে মার্ক্স পড়ানো হয়, তারা কেউ বিপ্লবী হয়ে যায় না। তারা কেউ কলেজের সিলেবাসে মার্ক্স পরে সমাজ পাল্টাতে যায় না।
২
২০৫০এর ভারতবর্ষের এক ভীষণ ছবি আমি চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাই। সেই ছবি যে সত্যের ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সত্যের প্রাথমিক সন্ধান আমাকে দিয়েছে পরিবেশবিদ্যার মত একটা বৈজ্ঞানিক ডিসিপ্লিন। অথচ মজার ব্যাপার হলো, সেই সত্য এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে এমন অদ্ভুতভাবে পরিবেশিত যে, তা সেই জ্ঞান অন্বেষণকারীকে (খুব ব্যতিক্রমী না হলে) অবশ্যম্ভাবীভাবে আন্দোলন বিমুখ করে তোলে।
আসলে জ্ঞান নামক বস্তু যখন পণ্যে পরিণত হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই সেই জ্ঞানের মাহাত্ম পণ্যের মহাত্মে পরিণত হয়।
আমাদের দেশ কেন, সারা পৃথিবীতেই ছাত্রছাত্রীরা এখন নিছক ডিগ্রির প্রয়োজনে কলেজে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এবং তারা সেইসব বিষয়ই পড়তে আগ্রহী যেসব বিষয়ের বাজারে চাহিদা বা ‘দাম’ আছে। পরিবেশ সংকট সন্দেহাতীত ভাবে পরিবেশ সংক্রান্ত যেকোন বিদ্যার ‘দাম’ বা বাজারমূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে, সে পরিবেশ বিজ্ঞান হোক বা পরিবেশ বিদ্যা। সে পরিবেশ ইঞ্জিনিয়ারিং হোক বা পরিবেশ ম্যানেজমেন্ট।
পরিবেশ বিজ্ঞানের জ্ঞানের বিষয় পরিবেশ। এই ডিসিপ্লিনটি বৈজ্ঞানিক পরিসরে, অর্থাৎ, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজির সূত্র (law) মোতাবেক, পরিবেশ নামক বস্তুটিকে (objectটিকে) বস্তুনিষ্ঠভাবে (objectively) জানতে, বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে।
পরিবেশ বিদ্যা পরিবেশ বিজ্ঞানের সেই objective তথা scientific truthকে মানব বিজ্ঞানের (যেমন অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইত্যাদি) বিভিন্ন লেন্স মারফত জানতে, বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে।
পরিবেশ ইঞ্জিনিয়ারিং পরিবেশ বিজ্ঞানের সেই objective তথা scientific truthকে technology প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে manipulate করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলে।
পরিবেশ ম্যানেজমেন্ট আরেকটু এগিয়ে গিয়ে পরিবেশ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সেই ব্যবহার উপযোগী করে তোলা পণ্যের উৎপাদন, বন্টন, বিপণন, ইত্যাদি কিভাবে করা যেতে পারে তা জানতে বুঝতে চেষ্টা করে।
অর্থাৎ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চা ছাত্রছাত্রীদের (অর্থনীতির ভাষায়) মানবসম্পদে (human resourceএ) পরিণত করে। এই পরিসরে ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশ সংক্রান্ত এমনই জ্ঞান আরোহণ করে যা মূলত রাষ্ট্র ও বাজারের কাজে লাগে। এবং সেই জ্ঞান এমনভাবেই উৎপাদিত ও পরিবেশিত হয় যাতে ছাত্রছাত্রীরা তা তাদের পরবর্তী জীবনে বিক্রয় করে (অর্থাৎ, চাকরি করে) সচ্ছলভাবে জীবন নির্বাহ করতে পারে। অর্থাৎ, বাজারে উৎপন্ন অন্যান্য সমস্ত পন্যাদির উপযুক্ত উপভোক্তা হতে পারে।
৩
এহেন জ্ঞান-পণ্যের পরিসরে ক্রয়বিক্রয়ের অধিক কিছু আশা করা বাতুলতা মাত্র। শুধু তাই নয়, এহেন জ্ঞান, যা পুঁজির যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত, যা বাজারের মূল্যবোধে সিক্ত, যা প্রকৃতিকে নিছক উৎপাদনের উপকরণ (natural resources) হিসেবে দেখে, যা বাস্তুতন্ত্রকে (অর্থনীতির ভাষায়) সেবাদ্রব্য (ecosystem services) জ্ঞান করে, এবং যা শুধুমাত্র পরিশেষে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসনই করতে চায়, সেই জ্ঞান পরিবেশ আন্দোলনের ক্ষেত্রে শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, বিপদজনকও বটে।
তাই বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ নির্মাণের সম্ভাবনা আগেই খারিজ করে দিয়েছিলাম। এবং তার বিকল্প হিসেবে আমি এক ভবিষৎবাদী সত্যনির্ভর কল্পকাহিনী রচনার কথা ভাবছিলাম (খানিকটা রাহুল সংকৃত্যায়নের ভোলগা থেকে গঙ্গার ঢঙে)। সেরকম কাহিনী নির্মাণ নিশ্চিতরূপে সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন তার থেকেও গুরুতর।
জীবনের প্রতি আমার সাধারণ বা সর্বমোট প্রশ্ন হচ্ছে: আমি যা করছি তা কেন করছি? কি উদ্দেশ্যে করছি?
আর এক্ষেত্রে আমার সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন হচ্ছে: এরকম কোন লেখা আমি লিখতেই পারি, কিন্তু কেন লিখবো? কি উদ্দেশ্যে লিখবো?
এই উদ্দেশ্যটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।
৪
ইউরোপীয় আধুনিকতা পুরোনো যা কিছু, সে ধ্যানধারণা হোক বা অনুশীলন, তাকে ঠেলে ফেলে তার জায়গায় নতুন কিছু করার প্রস্তাব করে। ঠিক সেই জায়গা থেকে এহেন আধুনিকতা তার ঐতিহাসিক সময়ের কাছে এক নতুন ধরনের শিল্পেরও দাবি নিয়ে হাজির হয়।
আধুনিকতা একটি বিমূর্ত ধারণা মাত্র। তাই তাকে কোন একটি মাত্রায় ধরা মুশকিল। তার যেমন একটি দার্শনিক দিক আছে, সেরকমই তার একটি বৈজ্ঞানিক দিক আছে। তার সাথে তার একটি প্রযুক্তির দিকও যেমন আছে, সেরকম একটি শিল্পের দিকও আছে। আবার একইসঙ্গে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকও আছে। এই সব মিলিয়ে ইউরোপীয় আধুনিকতা।
এহেন ইউরোপীয় আধুনিকতার প্রধান দার্শনিক ইম্যানুয়েল ক্যান্ট। তিনি তার Critique of Judgement (১৭৯০)এ যে নান্দনিক তত্ত্ব পেশ করলেন তার অর্থ খানিকটা এরকম: আমরা যখন কোনো একটি বস্তুকে সুন্দর বলে জ্ঞান করি, তখন আমাদের মনে হয় যেন সেই বস্তুটি তার রূপের অন্তিমে (finalityতে) এসে পৌঁছেছে। মনে হয় যেন সেই রূপ কোনো এক বিশেষ (অলৌকিক) উদ্দেশ্যে অভিপ্রেত। যদিও বাস্তবে তার কোনো ব্যবহারিক কার্যকারিতা নাও থাকতে পারে।
এই যে কোনোরকম ব্যবহারিক কার্যকারিতাবিহীন সৌন্দর্যের ধারণা, এটার জন্যই যেন গোটা ইউরোপ অপেক্ষা করে ছিলো। এবং যা কালক্রমে হয়ে উঠলো ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পসাহিত্যের বৌদ্ধিক মানদন্ড।
৫
উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে শিল্প ও সাহিত্য সংক্রান্ত পুরোনো যা কিছু ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ, তাকে দূরে ঠেলে ফেলে ইউরোপীয় শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকরা নতুন ধরনের, তথা আধুনিক শিল্পসাহিত্যের সাধনায় ব্রতী হন। এই আধুনিক
শিল্প ও সাহিত্য সাধনার প্রধান স্লোগান হয়ে উঠে “শিল্পের তাগিদে শিল্প” (art for the sake of art)।
তাদের বক্তব্য ছিল, শিল্প ও সাহিত্য হবে স্বাধীন। তার কোনো দায় থাকবেনা। না ধর্মের কাছে, না রাজনীতির কাছে, না নীতিনৈতিকতার কাছে। শুদ্ধ শিল্পকর্ম। শিল্পগুনের অধিক কোনো কার্যকারিতা তার না থাকলেও চলবে।
এহেন শিল্প ও সাহিত্য ভাবনার প্রধান দুজন তাত্ত্বিক কারিগর Théophile Gautier এবং Edgar Allan Poe হলেও, তার বৌদ্ধিক ক্ষেত্র ক্যান্ট আগেই রচনা করে গেছিলেন।
৬
কিন্তু ওই যে বলছিলাম, আধুনিকতা একটি বহুমাত্রিক ব্যাপার। এখানে দর্শন, বিজ্ঞান,
শিল্পসাহিত্য, প্রযুক্তি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সবকিছু জড়িয়েপেঁচিয়ে আছে। তাই শুধু দর্শন বা শিল্পসাহিত্য দিয়ে তাকে বুঝতে গেলে সে বোঝা নিশ্চিন্তে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।
এই তথাকথিত শুদ্ধ শিল্পকর্মের ধারণাটি অচিরেই পুঁজির কাছে খুব লোভনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এবং আধুনিকতার টানাপোড়েনে “শিল্পের তাগিদে শিল্প” (art for the sake of art) কালক্রমে হয়ে ওঠে “বাজারের তাগিদে শিল্প” (art for the sake of market)।
আধুনিকতার ইতিহাসে পুঁজি এবং প্রযুক্তি হাতে হাত ধরে এগিয়েছে। এবং প্রযুক্তি যে শুধু আধুনিক শিল্পসাহিত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে পুঁজির সহযোগী হয়েছে তাই নয়, সে নতুন ধরনের শিল্প উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে আধুনিক উপন্যাসের কথা, যার উদ্ভব ও বিস্তারের ইতিহাস আধুনিক প্রিন্ট প্রযুক্তি ও প্রিন্ট পুঁজিবাদের ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।
একইভাবে বলা যেতে পারে সিনেমার কথা, যার উদ্ভব ও বিস্তারের ইতিহাস একইভাবে আধুনিক চলমান ক্যামেরা প্রযুক্তি ও বিনোদন পুঁজিবাদের ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।
অর্থাৎ, আধুনিক শিল্প ও সাহিত্য পুঁজি ও প্রযুক্তির প্যাঁচে পরে অচিরেই তার ‘শুদ্ধ শিল্পকর্ম ও সাহিত্যকর্ম’ থেকে স্খলিত হয়ে শিল্পপণ্যে ও সাহিত্যপণ্যে রূপান্তরিত হলো। তার সাথে তার শিল্প ও সাহিত্যের মাহত্য পরিণত হলো পণ্যের মহাত্যে। একে আধুনিকতার ট্রাজিডি হিসেবে দেখা যেতে পারে। কারণ এর সাথে পণ্যে পর্যবসিত হলো শিল্প ও সাহিত্যের যাবতীয় মহৎ আবেগ ও অনুভূতি, ধারণা ও কল্পনা, বিপ্লব ও আদর্শ।
হ্যাঁ, এর সাথেই পণ্যে পর্যবসিত হলো শিল্প ও সাহিত্যের যাবতীয় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সংকল্প।
৭
এরকম একটা পণ্যসংস্কৃতির আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে মনে হলো, যে আপাত সহজ লেখালেখি সংবলিত কাজটি আমি করবার পরিকল্পনা করছি তা বাস্তবে আশাতীত রকমের জটিল।
জটিলতার প্রথম কারণ, প্রযুক্তি ও পুঁজি একে অপরের সাথে জড়িয়ে পেঁচিয়ে (entangled হয়ে) আছে। প্রযুক্তি ও পুঁজির এই entanglementএর কল্যানে আমাদের প্রায় সমস্ত আদানপ্রদান, প্রায় সমস্ত জ্ঞাপন (communication) প্রকৃতপ্রস্তাবে পণ্য সংবহনে (commodity circulationএ) পরিণত হয়েছে। বা উল্টোদিক থেকে বলা যেতে পারে, পণ্য সংবহন আমাদের যাবতীয় আদানপ্রদানের ও জ্ঞাপনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। সে দার্শনিক জ্ঞাপন হোক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞাপন, সে শৈল্পিক জ্ঞাপন হোক বা সাহিত্যিক জ্ঞাপন, সে রাজনৈতিক জ্ঞাপন হোক বা সামাজিক জ্ঞাপন।
অর্থাৎ, আমরা মানুষ, আমরা কথাবলা প্রাণী। দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই কথাবলার গোটা জগৎটা, আদানপ্রদানের গোটা জগৎটা, ভাব বিনিময়ের গোটা জগৎটা পুঁজির দখলে চলে গেছে। এবং পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে যে সেই জগৎ পুঁজির দ্বারা প্রভাবিত, পুঁজির মূল্যবোধে সিক্ত, পুঁজির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
৮
জটিলতার দ্বিতীয় কারণ, এরকম একটি সর্বব্যাপী পণ্যসংস্কৃতির বাতাবরণের ভেতর দাঁড়িয়ে আমার এই বিশেষ কাজের (বা এই লেখার) অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এবং এই বিশেষ উদ্দেশ্যটির কারণেই এতসব কথা এসে পড়ছে।
আমার উদ্দেশ্যতো আসলে বর্তমানের সর্বগ্রাসী পরিবেশ সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিরোধমূলক পরিবেশ আন্দোলন গড়ে তোলা।
আর তার জন্য মানুষের কাছে পৌঁছনো দরকার। তাদেরকে বলা দরকার যে আমাদের মাথার ওপর মহাপ্রলয় নাচানাচি করছে। অবশ্যম্ভাবী পরিবেশ বিপর্যয় আমাদের দুয়ারে করা নাড়ছে।
কিন্তু নিছক বলা দরকার এমনটা নয়। শুধু বলে কাজ হবেনা। মানুষকে sensitize করা দরকার। পরিবেশ সংকটের প্রশ্নে এই sensitizationই সব থেকে বড় challenge, কারণ পরিবেশ তথা পরিবেশ সংকটের প্রশ্নে মানুষ একধরনের উদাসীনতার অসুখে ভুগছে।
ভেবেচিন্তে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, এই পরিবেশ উদাসীনতার অসুখটি ultimately বৃহত্তর পরিবেশ অ-সুখেরই অংশ। এবং এটা এমন একটি অদ্ভুত অসুখ, যা আমাদের ওই সর্বগ্রাসী পরিবেশ অ-সুখের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে অন্যতম প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
অতএব এই বাধা দূর করা প্রয়োজন।
৯
আমরা এই স্বল্প পরিসরে এই পরিবেশ উদাসীনতার অ-সুখটিকে বৌদ্ধ দুঃখ সত্যের জায়গা থেকে খানিকটা বুঝতে চেষ্টা করতে পারি।
বুদ্ধ বলছেন যে আমরা সংসারের ফাঁদে আটকে পরে আছি। সংসার দুঃখময়। এর দুঃখ তো দুঃখের বটেই, এর আপাত সুখও আখেরে দুঃখের, কারণ সংসার অনিত্য। তাই সুখও অনিত্য। আর আমরা এই অনিত্যের সংসারে নিত্য সুখের তৃষ্ণায় আরো বেশি বেশি করে দুঃখকে ডেকে অনি।
বুদ্ধ এসব কথা বলেছেন ২৬০০ বছর আগে। তার এই কথা যদি আজকের সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি তাহলে আমরা এরকম ৮০০ কোটি গল্প পেতে পারি। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের একটি করে গল্প। তাদের নিজের জীবনের গল্প। প্রতিটি গল্পই অনন্য। কিন্তু প্রতিটি গল্পই দুঃখের।
বুদ্ধের কথা অনুযায়ী, এই প্রতিটি দুঃখের গল্পের একটি জায়গায় ভীষণ মিল আছে। এই প্রতিটি গল্পের প্রধান চরিত্ররা অনিত্যের সংসারে নিত্য সুখ খুঁজেছিলো। বা বলা ভালো, তারা সবাই নিজের, তথা নিজের প্রিয়জনের নিত্য সুখ সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিল।
নারী পুরুষ নিত্য সুখের সন্ধানে প্রেম করে। নিত্য সুখের সন্ধানে তারা রোজকার করার চেষ্টা করে। নিত্য সুখের সন্ধানে তারা বিবাহ করে। নিত্য সুখের সন্ধানে তারা সন্তানের জন্ম দেয়। তারপর সেই সন্তানের নিত্য সুখ সুনিশ্চিত করবার আসায় তাকে ভালো করে পড়াশোনা করায়। সেই সন্তানও বড় হয়ে নিত্য সুখের সন্ধানে প্রেম করে। নিত্য সুখের সন্ধানে সেও রোজকার করার চেষ্টা করে। নিত্য সুখের সন্ধানে সেও বিবাহ করে। নিত্য সুখের সন্ধানে সেও সন্তানের জন্ম দেয়। এভাবেই চলে, চলতে থাকে, চলতেই থাকে। এই চক্রাবত বিন্যাসকে (এই cyclic orderকে) বুদ্ধ সংসার বলেছেন।
একটু ভালো করে দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে এই নিত্য সুখের সন্ধানই এই চক্রাবত বিন্যাসের, তথা এই সংসারের চালিকা শক্তি। আর এই অনিত্যের সংসারে নিত্য সুখের তৃষ্ণা, তথা নিত্য সুখের সন্ধানই আমাদের দুঃখের কারণ।
এবং শুধু তাই নয়, যে নিত্য সুখের তৃষ্ণা, বা নিত্য সুখের সন্ধান আমাদের দুঃখের কারণ, সেই দুঃখকে ঘোচানোর তাগিদে আমরা আরো বেশি বেশি করে নিত্য সুখের সন্ধানে ব্রতী হই। তার ফলে আমাদের দুঃখ কমা দূরে থাক, আরো বেড়ে বেড়ে যায়।
১০
বুদ্ধ কথিত সংসার নামক যে চক্রাবত বিন্যাসের পাকেচক্রে আটকে পড়ে আমরা দুঃখের জীবন কাটাই, আজকের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে আমরা পণ্য সংবাহনের চক্রাবত বিন্যাস হিসেবে দেখতে পারি।
আমাদের ‘মানুষ’ হওয়া তো প্রকৃতপ্রস্তাবে নিজেদের উপযুক্ত মানবসম্পদ নামক পণ্যে পরিণত করা। আমাদের কাজ, সে জ্ঞানচর্চা হোক বা শিল্পসৃষ্টি, প্রকৃতপ্রস্তাবেতো তা পণ্য উৎপাদন মাত্র। আমরা যাকে জীবন বলে জানি, প্রকৃতপ্রস্তাবে তা পণ্য উপভোগ (consumption) ছাড়া আর বেশি কিছু কি?
অর্থাৎ, পণ্য সংবাহনের চক্রাবত বিন্যাসের পাকেচক্রে আটকে পড়ে আমরা নিজেরা প্রথমে পণ্যে পরিণত হই, তারপর বাকি জীবনটা পণ্য উৎপাদনে করে আর পণ্য উপভোগ করে কাটাই।
এই পণ্য সংবাহনের চক্রাবত বিন্যাসের পাকেচক্রে আটকে পড়ে আমরা নিঃসন্দেহে দুঃখের জীবন কাটাই। এবং এই পণ্য সংবাহনের দুর্বার গতি মানুষকে এবং তার পরিবেশকে (অর্থাৎ তার প্রকৃতি ও সংস্কৃতিকে) এক ভয়ংকর দুঃখে (বৌদ্ধ অর্থে দুঃখ) নিমজ্জিত করেছে।
আরো বড় কথা হলো এই পণ্যের পাকেচক্রে পরে তারা (বিশেষত ৮০এর দশকের মধ্যভাগ থেকে) এমন এক অবিদ্যার (বৌদ্ধ অর্থে অবিদ্যা) শীতঘুমে তলিয়ে গিয়েছে যে তাদের ঘুম ভাঙানো পরিবেশ কর্মীদের পক্ষে এক অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।
১১
১৯৭৯এ গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন মার্গারেট থ্যাচার। ১৯৮১তে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন রোনাল্ড রেগান। তার সাথে জার্মানিতে হেলমুট কোল আর ফ্রান্সে ফ্রাঁসোয়া মিতেরা। এদের হাত ধরে গোটা পৃথিবীতে এক নতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, তথা সাংস্কৃতিক বিন্যাস স্থাপিত হয় যাকে আমরা নব্য উদারনীতিবাদ বলি। এ জ্ঞান, পুঁজি ও প্রযুক্তির এক দুর্নিবার ক্ষমতাশালী শাসন প্রক্রিয়া (governmentality, ফুকোর অর্থে)।
ফুকোর ব্যাখ্যা অনুযায়ী নব্য উদারনীতিবাদ মূলত সক্রিয় বাজার সৃষ্টির রাজনীতি (active politics of market construction), যেখানে রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে বাজার সৃষ্টিতে মদত দেয়।
উদাহরণস্বরূপ দেখা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সাস্থসাথী কার্ড বা স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের প্রকল্পগুলোকে। সাস্থসাথী কার্ড প্রকল্প যেমন ভালো সরকারি হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরির বদলে সাস্থ পরিষেবার বাজার সৃষ্টিতে মদত দেয় সক্রিয়ভাবে। আর স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প যেমন ভালো সরকারি স্কুলকলেজ তৈরির বদলে শিক্ষা পরিষেবার বাজার সৃষ্টিতে মদত দেয় সক্রিয়ভাবে।
দ্বিতীয়ত, ফুকো বলছেন যে নব্য উদারনীতিবাদ শাসনের প্রশ্নে একধরনের পরিবেশগত প্রযুক্তি ব্যবহার করে। অর্থাৎ, সে এমন এক রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে যার ফলে নব্য উদারনীতিবাদী প্রজা (neoliberal subject) স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বাজারঅভিমুখে ধাবিত হয়।
এই বিশেষ পরিবেশগত প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে সেই
নব্য উদারনীতিবাদী প্রজা নিজেকে আপাতভাবে স্বাধীন অনুভব করে, যা প্রকৃতপ্রস্তাবে বাজারের স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু নয়।
এই পণ্য সংবাহনের চক্রাবত বিন্যাসের পাকেচক্রে আটকে পড়া, অবিদ্যার (বৌদ্ধ অর্থে অবিদ্যা) শীতঘুমে তলিয়ে যাওয়া, বাজার অভিমুখী নব্য উদারনীতিবাদী প্রজারাই আসলে সেই সংবেদন হারানো মানুষজন যারা পৃথিবীর গভীর গভীরতর অ-সুখ জেনেও উদাসীনভাবে মুখ ফিরিয়ে থাকে।
তারা তাদের অবিদ্যার কারণে জানেনা যে এই মুখ ফিরিয়ে থাকা, এই উদাসীনতা আসলে নিজেই একটা অসুখের লক্ষণ, পৃথিবীর গভীরতম অসুখের প্রতি সংবেদনশীলতা হারানোর লক্ষণ।
১২
এই পণ্য সংবাহনের চক্রাবত বিন্যাসের পাকেচক্রে আটকে পড়া মানুষের অবিদ্যার শীতঘুম কোনো পণ্য উপভোগ (consumption) মারফত ভাঙানো সম্ভব নয়। তা যদি সম্ভব হতো তাহলে তা এতদিনে অমিতাভ ঘোষের অনবদ্য লেখা, The Great Derangement, বা The Nutmeg’s Curse পড়ে মানুষের ঘুম ভাঙত, মানুষ পথে নামতো। পরিসংখ্যান বলছে ওগুলো ব্যবসা করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু মানুষের ঘুম কতটুকু ভাঙাতে পেরেছে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ওদুটো লেখা বিশ্বজোড়া পণ্য সংবাহন ব্যবস্থায় আর দুটি পণ্য হিসাবে নিজেদের যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষ পণ্যের যুক্তি মেনে তাদের উপভোগও (consume) করছে। যেভাবে বিজ্ঞানের উপভোক্তা বিজ্ঞান পণ্য উপভোগ করে, বা দর্শনের উপভোক্তা দর্শন পণ্য উপভোগ করে। আলাদা করে এই যুক্তির বাইরে শিল্প ও সাহিত্য পণ্যের উপভোক্তাদের বেরোনোর সুযোগ খুবই কম, সে তারা চায়ের কাপে যত বড়ই ঝড় তুলুননা কেন।
আসলে আমাদের বুঝতে হবে যে পণ্যের এই যুক্তি এক নিষ্কাশনমূলক (extractive), ভোগবাদী (consumerist) ও অপচয়মূলক (wasteful) সংস্কৃতির জাল বিস্তার করেছে। যে সংস্কৃতির মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য, সবই পরে এবং যারা একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েপেঁচিয়ে আছে। সেই প্রলয়ংকরী সংস্কৃতিই এই সজীব গ্রহের বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।
তাই পণ্যের যুক্তির বাইরে আমাদের বেরোতে হবে। বেরোতেই হবে। অর্থাৎ, আমাদের নতুন কোনো উপায়ের কথা ভাবতে হবে যা দিয়ে আমরা পণ্যের যুক্তিকে পাস কাটিয়ে যেতে পারি।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি হতে পারে সেই উপায়?
১৩
ঘুমিয়েপড়া মানুষকে জাগানোর একটি উপায় আজ থেকে ৫০০ বছর আগে চৈতন্যদেব আমাদের দেখিয়ে গেছেন এই বাংলায়। আর সেটা হচ্ছে পারফরম্যান্স। হ্যাঁ, একসাথে হৈ হৈ করে কীর্তন করতে করতে ঘুরে বেড়ানো তো পারফরম্যান্স বটেই। একেবারে সবাইমিলে একসঙ্গে (যৌথ) পারফরম্যান্স।
পারফরম্যান্স এক বিশেষ পরিসর তৈরি করে। যে পরিসরে পারফরম্যান্স চলাকালীন পারফরম্যান্স ব্যতিরেকে পারফরমারের ওপর অন্য কোনো শক্তি বা প্রভাব (যেমন পুঁজির শক্তি বা পণ্যের প্রভাব) সেভাবে কাজ করতে পারে না। পারফরমার পারফরমেন্সের ভেতর হারিয়ে যায়।
বৌদ্ধ ভাবনা অনুযায়ী, যেহেতু এই শিল্প কর্মে শিল্পীর পঞ্চস্কন্ধ (অর্থাৎ, বৌদ্ধ মতে তার whole person) যুক্ত হয়ে পড়ে, তা একধরনের ধ্যানে (meditative exerciseএ) পরিণত হয়। তাই সে সেই সময়ের জন্য পণ্য সংস্কারের (বৌদ্ধ অর্থে সংস্কারের) বাইরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। ঠিক যেমন কীর্তনের সময় কীর্তনকারীরা সমস্ত জাগতিক নিয়মের উর্ধে উঠে রাধা অঙ্গে বিলীন হয়ে যায়।
ফুকোর সূত্র ধরে পারফরম্যান্সকে একধরনের Heterotopia বলে ভাবা যেতে পারে। অর্থাৎ, পৃথিবীর ভেতর এমন এক পৃথিবী, যেখানে পৃথিবীর সব নিয়ম কানুন লাগু হয়না। অন্তত ওই সময়ের জন্য হয়না।
এই জায়গা থেকে চৈতন্যদেবের জনজাগরণের ওই মোক্ষম পদ্ধতিটিকে আমরা নিশ্চিন্তে পরিবেশ আন্দোলনে কাজে লাগাতে পারি। অন্তত মানুষের ঘুম ভাঙানোর প্রশ্নে, সর্বোপরি মৃতজনে প্রাণ সঞ্চারের প্রশ্নে এর থেকে শক্তিশালী অস্ত্র আর কিছু হতে পারে না।
১৪
আজ থেকে ২৮/৩০ বছর পরে, অর্থাৎ ২০৫০ শাল নাগাদ, এই দেশের যে অবস্থা হতে যাচ্ছে, তার ভয়ংকর ছবিটা আমি চোখ বন্ধ করা মাত্র দেখতে পাই। আর ভেতরে শিউরে শিউরে উঠি।
তখন আমরা অনেকেই হয়তো থাকবো। বৃদ্ধ এবং অসহায়। আমাদের সন্তানেরা হয়তো আমাদের আজকের বয়সে এসে পৌঁছাবে। তখন তারাই হবে এই ভবিষ্যত বিদ্ধস্ত প্রজাতন্ত্রের নাগরিক।
যে সব বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার নিরিখে আমার এই সত্যকল্পনা, অর্থাৎ যেসকল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও তথ্যের নিরিখে এহেন মহাপ্রলয়ের ছবি আমার চোখে ভেসে বারংবার উঠছে, তার একটা তালিকা এরকম হতে পারে:
১। সমুদ্রে জলস্তর বাড়ছে। ভারতবর্ষের তটরেখা গুজরাট থেকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত প্রায় ৭৫০০ কিলোমিটার। IPCC বলছে সমুদ্র অচিরেই উপকূলীয় সমভূমি গ্রাস করবে। Climate Central কম্পিউটার মডেলিং করে বছর ধরে ধরে বিপর্যয়ের মানচিত্র প্রকাশ করে দিয়েছে। বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাবে এতদঞ্চলের চাষবাস। মানুষ হারাবে তাদের জীবন ও জীবিকা। সুরাট, মুম্বাই, মাঙ্গালোর, কোচি, তিরুভান্তাপুরাম
চেন্নাই, ভিশকাপাট্টানাম ও কলকাতাসহ আরো বহু ছোটবড় শহর অবশ্যম্ভাবীভাবে জলের তলায় তলিয়ে যাবে। ডুবে যাবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ডুবে যাবে লাক্ষাদ্বীপ। উদ্বাস্তু হবে অন্তত ২০ কোটি মানুষ।
২। হিমবাহ গোলে যাচ্ছে। হিমালয়কে বলা হয় তৃতীয় মেরু (Third Pole)। কারণ উত্তরে আর্কটিক ও দক্ষিণে এন্টারর্কটিকের পরে এর মাথাতেই সবথেকে বেশি বরফ জমা থাকে। ২৫০০ কিলোমিটার দৈঘ্যের এই পাহাড়ে ৩২,০০০এর অধিক হিমবাহ আছে। তা সবই গলছে। অতি দ্রুতগতিতে গলে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের (তথা পৃথিবীর) অন্যান্য সমভূমি অঞ্চলের তুলনায় এখানকার উষ্ণায়নের হার প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি। তাই হিমবাহগুলো বছরে গড়ে ১৫ মিটার করে সঙ্কুচিত হচ্ছে। ব্রহ্মপুত্রের হিমবাহ সঙ্কোচনের হার বছরে ২০ মিটারেরও বেশি। হিমালয়ের বরফ গলে যে নদীগুলোর সৃষ্টি হয়েছে তার ওপর নির্ভর করেন ভারতবর্ষ সহ অন্যান্য আশেপাশের দেশসমূহের প্রায় ২০০ কোটি মানুষ। এই জমা বরফের ৪০% ইতিমধ্যেই গলে গাছে। ২০৫০ নাগাদ ৫০% অবধি বা তার অধিক গলে যাওয়ার সম্ভাবনা। তার ফলে প্রথমে বন্যা হবে। তারপর ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে সব নদীগুলো। ক্রমে জল কমে আসবে সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রসহ অন্যান্য নদীগুলোতে। তার সাথে তীব্র অভাব দেখা দেবে পানীয় জলের। চাষবাসের জন্য তো জল পাওয়া যাবেনা বললেই চলে। দুষ্কর হয়ে উঠবে এতদ সমভূমির কৃষি নির্ভর মানুষের জীবন ও জীবিকা। তার সাথে গোটা দেশজুড়ে দেখা দেবে সুতীব্র শক্তি সংকট। ভারতবর্ষের প্রায় ৭০% জলবিদ্যুৎ, তাপবিদ্যুৎ ও পারমাণবিকবিদ্যুৎ উৎপাদন হয় এইসব নদীর জল (অপ)ব্যবহার করেই।
৩। বিপর্যস্ত মৌসুমী বায়ু। আমরা জানি বাংলায় আষাঢ়, শ্রাবণ, এই দু মাস বর্ষাকাল। কিন্তু আজকাল আষাঢ় মাসে বৃষ্টির দেখা মেলেনা। বর্ষাকাল অন্তত মাসখানেক পেছনে সরে গেছে। শ্রাবণ মাস থেকে খাপছাড়া বৃষ্টি শুরু হয়। অর্থাৎ, বর্ষা ঋতু তার ছন্দ হারিয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের ফলে কয়েকদিন প্রবল বর্ষণের পরে লম্বা খরা। সেই ঝিরঝির করে বর্ষার বৃষ্টি আর নেই। এখন বৃষ্টি চলে আশ্বিন মাস অবধি। তারপরেও চলতে থাকে নিম্নচাপের আকস্মিক, অনিশ্চিত আক্রমণে। ভারতবর্ষের বৃষ্টিনির্ভর কৃষির দুরবস্থা চোখে দেখা যায়না। শুরুতে বৃষ্টির অভাবে বীজতলা জ্বলে যায়। আর শেষে ধান কাটার সময়ে বৃষ্টিতে ধান নষ্ট হয়ে যায়। বোঝাই যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে আর চাষবাস করা যাবেনা।
৪। অতিপ্রাকৃতিক বিপর্যয়। আয়লা থেকে আমফান, হুদহুদ থেকে ফনি, একেরপরএক যে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় বঙ্গোপসাগরের উপকূলে আছড়ে পড়ছে, যে বিপর্যয় ডেকে আনছে মানুষের জীবনে, তা অনস্বীকার্যভাবে অতিপ্রাকৃতিক। এর কারণ সরাসরিভাবে জীবাশ্মজ্বালানিকৃত বিশ্বউষ্ণায়ন। এর কারণ জীবাশ্মজ্বালানিনির্ভর অর্থনীতি। এর কারণ বিশ্বপুঁজিবাদ। আর শুধুমাত্র ঘূর্ণিঝড় নয়, এরকম অতিপ্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আরো বহুবিধ নিদর্শন আছে। যেমন আসামের অতিপ্রাকৃতিক বন্যা, মধ্যভারতের অতিপ্রাকৃতিক তাপপ্রবাহ, উত্তরভারতের অতিপ্রাকৃতিক শৈত্যপ্রবাহ, বা মহারাষ্ট্রের অতিপ্রাকৃতিক খরা ও বন্যা। এই চরম আবহাওয়া আগামী বিশতিরিশ বছরে তার চরমতম সীমায় পৌঁছাবে।
৫। চাষযোগ্য জমি মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। ভারতবর্ষের ৫২% চাষযোগ্য জমি মরুভূমি হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছে। এবিষয়ে ISRO এবং NASA বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানাসহ সবুজবিপ্লব বলয়ের আগামী ২০/২৫ বছরের মধ্যে মরুভূমির পরিণত হওয়ার পূর্বাভাস তো অনেক আগেই দেওয়া হয়েছিল। এখন এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়েছে ঝাড়খণ্ড, রাজস্থান, দিল্লি, গুজরাট এবং গোয়াসহ দেশের ৫২% জমি। আধুনিক কৃষির নামে জমির অপব্যবহার, বনজঙ্গল কেটে ফেলা, আর অস্বাভাবিক পরিমাণে ভৌমজল উত্তোলন, ইত্যাদি এর প্রধান কারণ। এই তালিকায় এখন যুক্ত হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটক। সুজলা সুফলা ভারতবর্ষ যদি মরুভূমি হয়ে যায় তাহলে এর বর্তমান ১৪০ কোটি, বা ভবিষ্যত ১৬৬ কোটি (২০৫০ শালের সম্ভাব্য জনসংখ্যা) জনগণের কি দুর্দশা হতে পারে তা কল্পনা করাও বেশ কঠিন।
৬। নদীগুলো একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী, একে একে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে। যত্রতত্র বাঁধ, অত্যাধিক মাত্রায় জল নিষ্কাশন আর ভয়ংকর দূষণ। তারওপর রয়েছে নদী থেকে যত্রতত্র মাটি, বালি আর পাথর চুরি। পবিত্র যমুনা আজ রাজধানী দিল্লির মলমূত্র বয়ে নিয়ে যায়। গঙ্গার দুর্দশা তো চোখে দেখা যায়না।
৭। ভৌমজলস্তর ক্রমশঃ নীচে নেমে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে খাওয়ার জল থাকবেনা। ২০৩০ শালে যে পরিমাণ পানীয় জলের প্রয়োজন, তার ৫০% জলও পাওয়া যাবেনা এদেশে। UNESCO বলছে যে আমরা পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বেশি ভৌমজল ব্যবহার করি। ফলে ভৌমজলস্তর ১ থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত নীচে নেমে যাচ্ছে প্রতিবছর। কৃষকেরা ভর্তুকির বিদ্যুৎ ব্যবহার করে জল তুলছেন। আর চালের মত water intensive crop (১ কিলো চাল উৎপাদন করতে ১৬০০ থেকে ২০০০ লিটার জল লাগে) উৎপাদন করে রফতানি করে দিচ্ছেন চড়া দামে।
৮। জঙ্গল সব শেষ হয়ে আসছে। অরণ্যবিনাশ সংক্রান্ত সরকারি তথ্য একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। সরকারি তথ্য বলছে দেশে অরণ্য আচ্ছাদন বাড়ছে। সরকার বুঝতে চাইছে না যে অরণ্য একটি বাস্তুতন্ত্র। তাই অরণ্য নিধন করে, কটা গাছ কাটা গেলো তার গুন্তি করে, অন্য কোনো জায়গায় কিছু গাছ লিগিয়ে দেওয়াকে অরণ্য বলে না। তা plantation মাত্র। অন্যতম জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের অরণ্য পৃথিবীর ৮% উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসভূমি। তাছাড়া প্রায় ২৮ কোটি মানুষ এদেশে অরণ্যের ওপর নির্ভর করে জীবনধারণের জন্য। খাদ্য, জ্বালানি ও পশুখাদ্যের জন্য। সেখানে প্রতিদিন শুনতে পাই আজ কয়লা তোলার জন্য (যেমন হাসদেও অরণ্য), কাল পাম তেল উৎপাদনের জন্য (যেমন উত্তরপূর্ব ভারতে), পরশু কোথাও রেল বা সড়ক যোগাযোগের জন্য (যেমন কেরালা, মুম্বাই, উত্তরাখন্ড) অরণ্য কেটে সাফ করা হচ্ছে।
৯। প্রায় প্রতিটি বাস্তুতন্ত্রই বিপর্যস্ত। শুধু অরণ্য নয়, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি বাস্তুতন্ত্রই কমবেশি বিপর্যস্ত, বিপন্ন। যেমন হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন, জোশীমঠের বিপর্যয় তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। তবে বোঝা যাচ্ছে যে শুধু যোশীমঠই নয়, বাস্তুতন্ত্রের বিপর্যয়ের কারণে এহেন বিপদের মুখে (তথা উন্নয়নের বলির মুখে) দাঁড়িয়ে আছে উত্তরাখণ্ডের অন্যান্য বহু শহর, যেমন কর্ণপ্রয়াগ এবং গোপেস্বর (চামলী), ঘানসালি (তেহারি), মুনসিয়ারি এবং ধরচুলা (পিথোরাগড়), ভাটওয়ারী (উত্তরকাশী), পাউড়ি, নৈনিতাল, ইত্যাদি। এর পাশাপাশি প্রতিটি নদী বাঁধ তার জলাধার সংলগ্ন অঞ্চলের বিস্তীর্ণ বাস্তুতন্ত্রের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়েছে। সুন্দরবন থেকে শুরু করে গুজরাট অবধি ম্যানগ্রোভ ও প্রবাল বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন। প্রতিটি নদীর বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন বাঁধ, দূষণ, নিষ্কাশনের চাপে। মাটির বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন সবুজবিপ্লবউত্তর কৃষির দাপটে। কোথাও গোটা পাহাড় কেটে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে মার্বেল আর গ্রানাইটের জন্য। এরপর আর কি পড়ে থাকে।
১০। শহরের বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না। দিল্লি শুধুমাত্র ভারতবর্ষের রাজধানী নয়, দূষণেরও রাজধানী এই শহর। মধ্যে ও দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ দূষিত ১৫টি শহরের মধ্যে ১১টি ভারতবর্ষে। প্রতিটি ভারতীয় শহরের দূষণের মাত্রা WHOএর বায়ুর গুনমানের নির্ধারিত সীমা (5 µg/m3) অতিক্রম করে বহুদূর। তার মধ্যে ৪৮% শহরে এই দূষণের মাত্রা ওই
নির্ধারিত সীমার ১০ গুনেরও বেশি। তার ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে COPD রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক। দশ লাখের ওপর মানুষ মাড়া যাচ্ছে প্রতিবছর বায়ু দূষণের কারণে। কুড়ি লাখের ওপর শিশু ভুগছে বিভিন্ন ধরনের ফুসফুসের অসুখে।
১১। অস্বাভাবিক শিল্পদূষণ। গত এক শতাব্দীতে ভারতবর্ষের শিল্প উৎপাদন ৫০ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে শিল্পদূষণ। Central Pollution Boardএর রিপোর্ট অনুযায়ী এইসব শিল্প কারখানার ৭৭% জলদূষণের জন্য দায়ী। ১৫% দায়ী বায়ুদূষণের জন্য। বাকি ৮% জল এবং বায়ু উভয়কেই দূষিত করে। এই রিপোর্ট আরো বলছে যে, যেসব শিল্প প্রকৃতির নিঃশর্ত দানকে যত বেশি (অপ)ব্যবহার করে, তারা তত বেশি দূষণ ঘটায়। এবং তাদের সংখ্যাই সবথেকে দ্রুত গতিতে বাড়ছে। তাছাড়া জলদূষণ ও বায়ুদূষণের পাশাপাশি আছে মৃত্তিকার দূষণ, উত্তাপজনিত দূষণ, পারমাণবিক দূষণ ও শব্দদূষণ। মূলত এধরনের দূষণের জন্য সবথেকে বেশি দায়ী অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, তামা কারখানাগুলো। তার সাথে অবশ্যই আছে বিদ্যুৎ ও সিমেন্ট। তাছাড়া আছে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার এবং লোহা ও ইস্পাত কারখানা। আর তৈল শোষণাগার, পেট্রোকেমিক্যাল ও ট্যানারি।
১২। দিকে দিকে আবর্জনার স্তুপ। ভারতবর্ষের শহরগুলোতে বছরে ৬.২ কোটি টন বর্জ্য উৎপাদন হয়। ২০৩০এ এই বর্জ্যে উৎপাদনের সম্ভাব্য পরিমান দাঁড়াবে ১৬.৫ কোটি টন। বর্তমানে যে বর্জ্য উৎপাদন হয় তার অর্ধেকই dump করা হচ্ছে কোনো না কোনো landfill siteএ। সেখানে জমে উঠেছে অস্বাস্থ্যকর আবর্জনার পাহাড়। হচ্ছে ভয়ংকর মৃত্তিকা দূষণ। এসব landfill siteএর মধ্যে আরব সাগরের গা ঘেষে গড়ে উঠা মুম্বাইয়ের দেওনার তো অতিকথায় পরিণত হয়েছে। তার ৩০০ একর বিস্তৃত landfillএ ১২০ ফুট অবধি উঁচু সারি সারি বর্জ্যের পাহাড় ভোগবাদী (অ)সভ্যতার কুৎসিততম নিদর্শন।
১৩। পরিবেশ ব্যাধির প্রাচুর্য। পরিবেশের অবনতি স্বাভাবিকভাবেই বহুবিধ রোগব্যাধির কারণ। বায়ু দূষণজনিত ফুসফুসের অসুখে মানুষের মৃত্যুর হার নিমুনিয়ার পরেই। তার পরেই স্থান জল দূষণজনিত অন্ত্রের বিভিন্ন অসুখের, যেমন ডায়রিয়া, কলেরা ও টাইফয়েড। তার সাথে গোলকের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বাড়বাড়ন্ত মশাবাহিত বিভিন্ন অসুখের, যেমন ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ও চিকেনগুনিয়া। কিন্তু এগুলোই সব নয়। এরসাথে আছে endocrinal malfunction (যেমন থাইরয়েড ও ডায়বেটিস), coronary heart disease এবং ক্যান্সার। তার সাথে উত্তরোত্তর বেড়ে চলা বিভিন্ন মানসিক ব্যাধি
১৪। বেড়ে চলা পরিবেশ উদ্বাস্তু। United Nations Refugee Agency (UNHCR)এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২১ শালে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এদেশে জলবায়ুপরিবর্তন ও অতিপ্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে। ভারতবর্ষের ৭৪% জেলা চরম আবহাওয়াজনিত বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে উড়িষ্যা, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।
১৫। বেড়ে চলা পরিবেশবিপর্যয়জনিত সংঘর্ষ। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের রিপোর্ট বলছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাড়ছে আত্মহত্যা, বাড়ছে অপরাধ, বাড়ছে হিংস্রতা, দাঙ্গা ও সংঘর্ষ। তারপর আছে দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রকৃতির নিঃশর্ত দানের ভাগ বাটোয়ারা সংক্রান্ত সমস্যা, যেমন কাবেরী জল বন্টন সমস্যা। সেরকমই আন্তর্জাতিক স্তরে তিস্তা জল বন্টন সমস্যা। কিন্তু এরও একটা ওপরের স্তর আছে। সেটা অনেক বেশি চিন্তার। যেমন পাকিস্তান সাথে প্রকৃতির নিঃশর্ত দানের ভাগ বাটোয়ারা সংক্রান্ত সমস্যা, যেমন সিন্ধু নদের জল, যা ভবিষ্যতে এই দুই দেশের মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধের কারণ হতে পারে।
১৫
এবারে ২০৫০এর ভারতবর্ষের ছবিটা আমাদের সত্যকল্পনায় এঁকে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হবেনা। কোটি কোটি বাস্তুচ্যুত মানুষ। ক্ষুধার্ত, কারণ বিপর্যস্ত কৃষি ব্যবস্থা, বিপর্যস্ত খাদ্য উৎপাদন। তৃষ্ণার্ত, কারণ দেশে পানীয় জল নেই। অর্থনীতি স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে পড়বে। আর দেশেতো এখন থেকেই জাতি দাঙ্গার বীজ বপন করে চলেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো।
অর্থাৎ পরিবেশ বিপর্যয়ের সাথে হতে হাত ধরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়। গৃহযুদ্ধ।
১৬
এই সত্যকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার পারফরমেন্স প্রকল্প। এবং তা হবে পরিবেশ আন্দোলনের ছোট ছোট গোষ্ঠীর সাথে হাতে হাত মিলিয়ে। এরা সবাই পরিবেশের একেকটি বিশেষ সমস্যাকে ঘিরে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এবং ওগুলো কোনো না কোনোভাবে উপরে আলোচিত ওই পনেরটি সমস্যার অংশ হতে বাধ্য। আমাদের কাজ হবে পারফরমেন্সের মধ্যে দিয়ে ওই প্রতিটি বিশেষ সমস্যাকে, ওই বৃহত্তর পনেরটি সমস্যার অংশ করে তোলা।
যেমন তিলাবনি পাহাড় বাঁচানোর আন্দোলন যে সমস্যাকে address করছে, বা মাথাভাঙ্গা ও চূর্ণী নদীর দূষণ বিরোধী আন্দোলন যে সমস্যাকে address করছে, সেই সমস্যাগুলোতো আসলে ওই বৃহত্তর পনেরটি সমস্যারই অংশ। অর্থাৎ, প্রতিটি বিশেষ সমস্যাকে ওই বৃহত্তর পনেরটি সমস্যার মধ্যে situate করা। তা করতে পারলে আমরা ভারতবর্ষের ২০৫০এর যে ছবি দেখতে পাচ্ছি তার detailsএর দিকগুলো আরো স্পষ্ট হযে উঠবে। আবার অন্যদিকে সেই আন্দোলন এই বৃহত্তর বিপর্যয়ের ছবির মধ্যে নিজেদেরকে খুঁজে পাবে।
সর্বোপরি এই পারফরমেন্স একটি বৃহত্তর পরিবেশ আন্দোলনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। সে কাঠবিড়ালির সেতুতে বালি দেওয়ার মত করে কাজ করলেও, করবে।
১৭
পারফরমেন্স বলতে একটা মিছিল। একটি লোক সাদা কাপড় গায়ে জড়ানো। তাতে রক্তের ছোপ। তার হাতে তার মায়ের, পৃথিবী মাতার রক্তাক্ত দেহ। সে হেটে যাচ্ছে। সাথে গান:
কাঁন্দি আমরা কাঁন্দি
ওরে, কাঁন্দি আমরা কাঁন্দি।
আকাশের লাইগ্যা কাঁন্দি আমরা
বাতারের লাইগ্যা কাঁন্দি,
মাটির লাইগ্যা কাঁন্দি আমরা
জলের লাইগ্যা কাঁন্দি।
কাঁন্দি আমরা কাঁন্দি
ওরে, কাঁন্দি আমরা কাঁন্দি।
কাঁন্দি আমরা হারায় যাওয়া পাখির কথা ভাইব্বা
কাঁন্দি আমরা হারায় যাওয়া নদীর কথা ভাইব্বা
জীবরনর লাইগ্যা কাঁন্দি আমরা
পৃথিবীর লাইগ্যা কাঁন্দি,
পাহাড় চূড়ায় হারায় যাওয়া বরফের লাইগ্যা কাঁন্দি
কাঁন্দি আমরা কাঁন্দি
ওরে, কাঁন্দি আমরা কাঁন্দি।
কাঁন্দি আমরা, কাঁন্দে অরণ্য, কাঁন্দে সমুন্দের জল
মানুরের চোখের জলে পৃথিবী হইবে কি শীতল
ওরে হইবে কি শীতল।
কাঁন্দি আমরা কাঁন্দি
ওরে, কাঁন্দি আমরা কাঁন্দি।
১৮
মিছিলের শেষে অভিজ্ঞতা বিনিময়, কথোপকথন, ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে গোটা narrativeটা তৈরি হবে। ঠিক জাল বোনার মত করে তৈরি হবে। তা নিয়ে পরবর্তী স্তরে তৈরি হবে একটা যৌথ লেখা। তৈরি হবে ভিডিও।
আরও পড়ুন – আমরা ৯৯%